সমুদ্রগুপ্তকে “ভারতের নেপোলিয়ন” বলা হয় কেন ?
সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন
প্রশ্ন। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা
অথবা,
সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা কর ।
অথবা,
বিজেতা হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্বের মূল্যায়ন কর। তাঁহার সাম্রাজ্যের আয়তন কি
অথবা, সমুদ্রগুপ্তকে “ভারতের নেপোলিয়ন” বলা হয় কেন ?
অথবা,
গুপ্তবংশীয় প্রথম তিন শাসকের অধীনে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তারের বিবরণ দাও।
অথবা,
সমুদ্রগুপ্ত কি ভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন ?
সমুদ্রগুপ্ত “ভারতের নেপোলিয়ন: উত্তর । কুষাণ সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলে উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছিল ঐ সাম্রাজ্যের পতনের পর তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় । বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে দেশ পুনরায় বিভক্ত সূচনা হইয়া পড়ে । কিন্তু গুপ্ত সম্রাটগণের নেতৃত্বে নূতন এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলে ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের
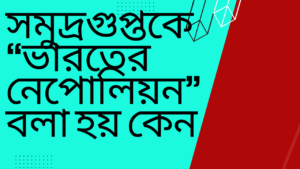
সমুদ্রগুপ্ত “ভারতের নেপোলিয়ন: গুপ্ত বংশের উৎপত্তি :
গুপ্ত বংশের উৎপত্তি বা উহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না বা এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণও সর্বত্র একমত নহেন । চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং (I-Tsing)-এর বিবরণে শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় । তিনি আনুমানিক ১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময় রাজত্ব করিতেন ।
সমসাময়িক লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মগধে মহারাজ গুপ্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। সম্ভবত অন্য কোনও রাজার সামন্তরাজ হিসাবে তিনি মগধের কোন এক ক্ষুদ্র অংশে রাজত্ব করিতেন । গুপ্তবংশের উৎপত্তি ও আদি বাসস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ দেখা যায় ।
ডঃ কে. পি. জয়সোয়ালের মতে গুপ্তরাজারা প্রথমে নাগ রাজবংশের সামন্ত হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন এবং প্রয়াগে বসবাস করিতেন । অ্যালানের মতে গুপ্তরাজারা সর্বপ্রথমে মগধে রাজ্য স্থাপন করেন। ডঃ ডি. সি. গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারণা, গুপ্তরাজাগণের আদি বাসস্থান মগধে ছিল না, ছিল বাংলার মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ।
ই-সিং-এর রচনা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার ভারত ভ্রমণের পাচশত বৎসর পূর্বে শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজা নালন্দার ২৪০ মাইল পূর্বে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন ।
রাজ্যের সীমা বিবরণে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশ গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিল। তাঁহার পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রথম ‘মহারাজাধিরাজ’ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে শুরু করেন। লিচ্ছবিরাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া তিনি শক্তিশালী হইয়া উঠেন ।
পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল । তিরহুত, এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও দক্ষিণ-বিহার পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল । সুতরাং প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাদেশের কিছু অংশে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হন। মৃত্যুর সময়ে তিনি তাঁহার পরাক্রমশালী পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান
সমুদ্রগুপ্ত :
এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি
এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সুযোগ্যপুত্র সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন । আনুমানিক ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ দেখা যায় ।
নালন্দার তাম্রলিপি অনুসারে জানা যায় যে, সম্ভবত ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন । ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে সমুদ্রগুপ্ত ৩২৫ হইতে ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সমুদ্রগুপ্ত ৩৪০ ও ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন ।
নানা দিক দিয়া সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে । এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ রাজকবি হরিষেণ রচিত প্রশস্তি, বিভিন্ন মুদ্রা ও লেখ, চৈনিক ঐতিহাসিকগণ রচিত গ্রন্থ প্রভৃতি উপাদান হইতে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।
সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় :
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে অগ্রসর হইলেন ।
(১) প্রথমেই তিনি আর্যাবর্তের রাজগণের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন । রুদ্রদেব, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মণ প্রমুখ নয়জন রাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি ঐ রাজ্যগুলি নির্জ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন ।
(২) এরপর তিনি মধ্য-প্রদেশের আটবিক রাজ্যসমূহ দখল করিয়া আপনসাম্রাজ্যবিস্তৃত করেন। এইভাবে তিনি ‘সর্বরাজোচ্ছেত্তা’র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্যাবর্তে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া তিনি দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন ৷
(৩) সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া তিনি কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজা, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ প্রমুখ বহু রাজাকে পরাজিত করিলেন । দক্ষিণ-ভারতের অভিযান সামরিক দিক হইতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিলেও তিনি ঐ সমস্ত রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন না, বরং স্থানীয় রাজগণের আনুগত্যের বিনিময়ে তাঁহাদের ঐ রাজ্যগুলি ফিরাইয়া দিলেন।
সম্ভবত সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ পাটলিপুত্র হইতে শাসন করা যথেষ্ট অসুবিধাজনক হইবে বুঝিতে দক্ষিণ-ভারতে তাহার নীতি’ পারিয়াই তিনি এই নীতি অনুসরণ করেন। এই পদক্ষেপ তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক ছিল ।
অন্যদিকে রোমিলা থাপারের মতে দক্ষিণ-ভারত অভিযানে সমুদ্রগুপ্ত আশাতিরিক্ত বিরোধীতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলিকে গুপ্তসাম্রাজ্যের মধ্যে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করেন নাই ।
দক্ষিণ-ভারতে সর্বমোট ১২টি রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। রাজ্যগুলি হইল—কৌশল, মহাকাস্তার, কৌরল, পিষ্টপুর, কটুর, এরওপল্ল, কাঞ্চি, পলাক্কা, দেবরাষ্ট্র, কুণ্ডলপুর । অভমুক্তা, বেঙ্গী,
সমুদ্রগুপ্তের সাফল্যের প্রভাব সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির উপরও পড়িয়াছিল ।
(৪) পূর্বসীমান্তে অবস্থিত নেপাল, কামরূপ, সমতট, দবাক ও কর্তৃপুর তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল । ঐ একই পথ অনুসরণ করিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণ ও গুজরাটের শকরাজগণ । বিভিন্ন গণতন্ত্রগুলিও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল ।
এইভাবে গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে কাশ্মীর, পশ্চিম-পাঞ্জাব, পশ্চিম-রাজপুতানা, সিন্ধু ও গুজরাট ভিন্ন প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।
উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনের এক্তিয়ার ভুক্ত ছিল । ইহা ছাড়া, দাক্ষিণাত্যের রাজগণ ও সীমান্তের অন্যান্য রাজ্যগুলি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন ।
সুতরাং সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ছিল প্রভুত্ব ও স্বায়ত্ত শাসনের এক অপূর্ব ও আশ্চর্য সমন্বয় । দ্বিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং এই যজ্ঞের স্মৃতিরক্ষার্থে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন ।
বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক :
সমুদ্রগুপ্তের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । মালব ও সৌরাষ্ট্রের রাজগণ তাঁহার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করিত ।
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশের কুষাণ-রাজ দৈবপুত্র শাহী তাঁহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল । সিংহলের রাজা মেঘবর্মণ বোধগয়ায় একটি সঙ্ঘরাম স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি চাহিয়া বহু উপঢৌকনসহ সিংহলের রাজা দক্ষিণ-পূর্বের দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।
সম্ভবত মালয় উপদ্বী সুমাত্রা ও যবদ্বীপের হিন্দু উপনিবেশগুলির উপরও তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল । সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁহার রাজ্যসীমার বাইরেও অনেকদূর বিস্তৃত হইয়াছিল ।
সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ
রাজ কবি হরিষেণ রচিত ‘এলাহাবাদ-প্রশস্তি’ হইতে সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে বহু কিছু জানিতে পারা যায়। তিনি কেবলমাত্র একজন দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ দিগ্বিজয়ী ও সুদক্ষ রাজ্যশাসক ।
দক্ষিণ-ভারতের রাজাদের সম্পর্কে তিনি যে মিত্ৰতামূলক নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কূটনৈতিক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে তাঁহার বাস্তব বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রতিফলন পড়িয়াছিল ।
সমুদ্র গুপ্ত কেবলমাত্র সুদক্ষ রাষ্ট্রশাসকই ছিলেন না; তিনি একাধারে বিদ্যোৎসাহী সুকবি ও সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন । তাঁহার সভায় জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ ঘটিত । তাঁহার মুদ্রায় বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্তের মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছিল । ‘এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে’ তাঁহাকে ‘কবিরাজ’ রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ।
ধর্মের দিক দিয়াও সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন উদার। তিনি নিজে ছিলেন’ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী এবং সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্মের ধর্মসম্বন্ধে উদারতা ‘পরমধর্মসহিষ্ণুতা’ নবজাগরণে তাঁহার দান ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ‘পরধর্মসহিষ্ণুতা’ ছিল তাঁহার ধর্মনীতির মূল কথা।
সিংহলের রাজা-মেঘবর্মণকে বোধগয়ায় মঠ নির্মাণ করিবার অনুমতি দিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই । বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধুকে তিনি অনায়াসে মন্ত্রিপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন ।
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের ভারত জুড়িয়া এক সার্বভৌম পর সমুদ্রগুপ্তই প্রথম সমস্ত রাজশক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যবিভক্ত ভারতে তিনি রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ।
অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও বৈদেশিক আক্রমণ এই দ্বিবিধ সমস্যার যথার্থ সমাধান করিয়া তিনি ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃস্থাপন করেন । এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় তিনি ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের সার্থক উত্তরসূরী । সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য বিস্তারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমিলা থাপার মনে করেন যে বর্ণ ও উপজাতির মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে যে দীর্ঘসংগ্রাম চলিতেছিল তাঁহার অবসান ঘটিল বর্ণের ঐক্য সৃষ্টি মুক্ত ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক সাফল্য সূচনা করে ।
ইহা ছাড়া শক ও কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী শাসন হইতে তিনি উত্তর-ভারতকে করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । এইজন্যই তিনি কেবলমাত্র গুপ্তবংশের নয়, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া তিনি গুপ্তসাম্রাজ্য দৃঢ়ভিত্তির উপর নরপতিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দাবি করিতে পারেন।
তাঁহার সামরিক অভিযানের ব্যাপকতা ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিস্তৃতি লক্ষ্য করিয়াই ডক্টর স্মিথ তাঁহাকে ‘ভারতের নেপোলিয়ন’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইওরোপের নেপোলিয়নে’র সহিত সমুদ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্য ও রাজনৈতিক প্রতিভার যে কিছু সাদৃশ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।
কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে পণ্ডিতসমাজে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ইওরোপের নেপোলিয়ন তাহা অর্জন করিতে পারেন নাই। ইহা ছাড়া নেপোলিয়নের মত তিনি পররাজ্য গ্রাস করেন নাই, ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সম্পন্ন করা তাঁহার রাজ্য বিস্তার নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ।
বস্তুতপক্ষে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ভারতের চিরায়ত আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল ।
সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন




