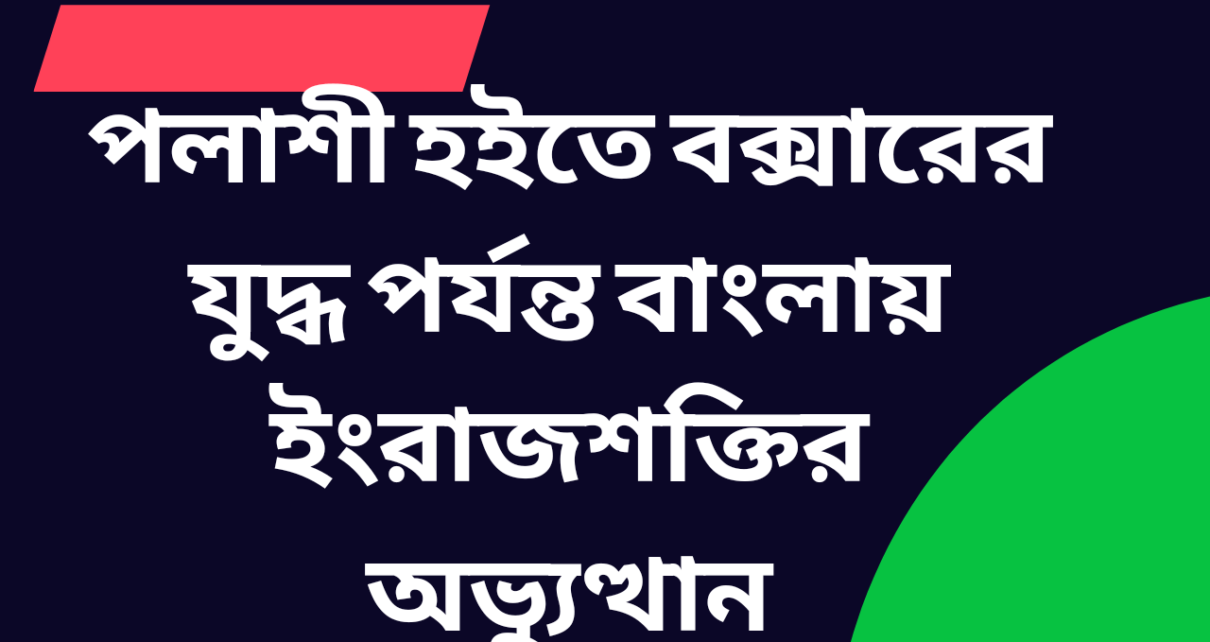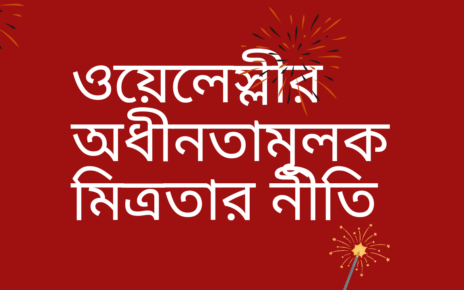পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজশক্তির অভ্যুত্থানের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি সংক্ষেপে লিখ
প্রশ্ন । মীরজাফর ও মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজদের সম্পর্ক আলোচনা কর।
অথবা,
১৭৫৬ হইতে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বাংলার নবাবদের সম্পর্ক পর্যালোচনা কর।
অথৰা,
পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজশক্তির অভ্যুত্থানের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি সংক্ষেপে লিখ।
অথবা,
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
অথবা,
পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজশক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী বর্ণনা কর। ইংরাজদের সাফল্যের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।
অথবা,
পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী প্রথম দশকে ব্রিটিশরা কিভাবে বাংলায় তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল?
পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ: উত্তর। প্রথম পর্যায় (১৭৫৬–১৭৫৭) ঃ
মীরজাফরের পরিচয়
পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ: জঘন্যতম ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও জালিয়াতির সাহায্যে সিরাজের পতন ঘটাইয়া যিনি বাংলার নবাব হইলেন তিনি হইলেন ইতিহাস বিখ্যাত মীরজাফর। তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দীর ভগ্নীপতি এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাঁহার সহকর্মী। আলিবর্দী অপুত্রক ছিলেন বলিয়া অন্যান্য অনেকের মত তিনিও সিংহাসন-লাভের আশা পোষণ করিতেন। সুতরাং সিরাজ-উদ্-দৌলা নবাব হইলে তিনি অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। এবং সিরাজের বিরুদ্ধে এক গোপন ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে দেখা দিলেন।
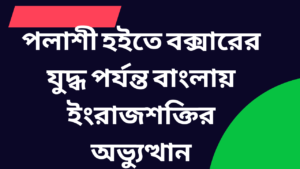
তিনি বিদেশী বণিক্ সম্প্রদায় ইংরাজদের সাহায্য গ্রহণেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। তিনি মুর্শিদাবাদে ইংরাজ প্রতিনিধি ওয়াটসন-এর মারফৎ ক্লাইভের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্জাবী বণিক শেঠ উমিচাঁদ-এর মাধ্যমে এই যোগাযোগ এক ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তিতে পর্যবসিত হইল। এই চুক্তি সম্পাদনে তিনি ক্লাইভের সহযোগে উমিচাদকে প্রতারিত করিবার জন্য জালিয়াতি পন্থা গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না।
সিরাজ সমস্ত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াও মীরজাফরের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না, বরং বারবার তাঁহার কাছে আবেদন করিলেন, তাঁহার মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশাত্ববোধ জাগ্রত করিবার জন্য। কিন্তু মীরজাফর সে সমস্ত বিসর্জন দিয়া সিরাজের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং পলাশীর প্রান্তরে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিলেন। *
দ্বিতীয় পর্যায় (১৭৫৭-১৭৬০ খ্রীঃ) :
বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও বিদেশীর সাহায্যে সিরাজের পতন ঘটাইয়া ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মীরজাফর বাংলার সিংহাসন দখল করিলেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি নানা সমস্যার সম্মুখীন হইলেন।
প্রথমত, ইংরাজদের সাহায্যের প্রতিদানে তিনি কোম্পানীকে, ক্লাইভকে ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীকে যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্ৰুত হইয়াছিলেন সেই বিরাট অর্থ তিনি রাজকোষে পাইলেন না; সুতরাং সরকারী সম্পত্তি পর্যন্ত তাঁহাকে বিক্রয় করিতে হইল, ক্লাইভ তাঁহাকে এতটুকু রেহাই দিলেন না।
দ্বিতীয়ত, আর্থিক অনটনের জন্য শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবার উপক্রম হইলে তিনি ধনী ব্যক্তি ও জমিদারগণের নিকট হইতে অন্যায় অত্যাচারের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইলেন; সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
তৃতীয়ত, এই সময়ে ঢাকা ও পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দেখা দিলে এই সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিনি আবার ক্লাইভ ও কোম্পানীর দ্বারস্থ হইলেন, ফলে তিনি তাহাদের কাছে আরও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এই অর্থ আদায়ে তাহারা এতটুকু তৎপরতার অভাব দেখাইল না।
মীরজাফরের আর্থিক দুরবস্থা ইংরাজদের অর্থলোলুপতা চরমে পৌঁছিল। ক্লাইভ বাৎসরিক ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের একটি জায়গির আদায় করিলেন। বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব কোম্পানীর নিকট বন্ধক রাখিতে হইল। কিন্তু ইংরাজদের অর্থলোলুপতা ও
ঔদ্ধত্য বাড়িয়া চলিল। এই সময়ের ইংরাজ কর্মচারীদের অর্থগৃধ্নতা ও নীচতা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণকেও লজ্জা দিয়াছে। *
কিন্তু মীরজাফরের মত হীনচেতা লোকের পক্ষেও ইংরাজ-ঔদ্ধত্য আর সহ্য করা সম্ভব হইল না। তিনি ইংরাজ শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য গোপনে ওলন্দাজগণের সহিত যোগাযোগ সৃষ্টি করিলেন। নিজেদের বাণিজ্যের স্বার্থেই ওলন্দাজগণ ইংরাজদের বিরুদ্ধাচারণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।
১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হুগলী নদীর মোহনায় ওলন্দাজ নৌবহর আসিয়া পৌছিলে উহা ক্লাইভ কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়, কারণ তিনি পূর্বেই যোগাযোগ সম্বন্ধে খবর পাইয়াছিলেন। ইত্যবসরে দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা পাটনা আক্রমণ করিলে ইংরাজদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া
ইংরাজদের নীতি ও অর্থলোলুপতার ফলেই নবাব-এর শাসনতন্ত্র ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ইংরাজগণ দেখিল যে মীরজাফর কোন দিক দিয়াই আর নির্ভরযোগ্য নয়।
** অবশেষে কলিকাতার তদানীন্তন গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট (Vansitart) নবাবের জামাতা মীরকাশিমের সহিত একটি গোপন চুক্তি সম্পাদন করিলেন। এই চুক্তি অনুসারে মীরকাশিম কোম্পানীর পূর্বের সমস্ত প্রাপ্যসহ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব কোম্পানীকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।
অতঃপর ইংরাজগণ তাহাদের পূর্বেকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া মীরজাফরকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া মীরকাশিমকে সেখানে বসাইলেন। কারণ নবাব পরিবর্তন তাহাদের নিকট একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ের ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীদের নীচ স্বার্থপরতা তাহাদের জাতির নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে।
তৃতীয় পর্যায় (১৭৬০-৬৪ খ্রীঃ), মীরকাশিম :
মীরকাশিম ছিলেন মীরজাফরের জামাতা। বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বরাবরই ছিল। বাংলার জটিল পরিস্থিতি ও মলিন পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি মীরজাফরের বিরুদ্ধে ইংরাজদের সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন এবং তাহাদেরই সাহায্যে বাংলার সিংহাসন দখল করিলেন।
কিন্তু ইংরাজদের সাহায্যে সিংহাসন দখল করিলেও তিনি ছিলেন মীরজাফর হইতে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মীরকাশিম ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিক। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে আর্থিক সঙ্কটই মীরজাফরকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল এবং ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজদের অর্থলোলুপতা ও দূরদর্শী রাজনীতিক দেশের সামরিক দুর্বলতা নবাবের স্বাধীন কার্যকলাপের পথে প্রধান বাধা। সেইজন্য তিনি কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করিলেন—(১) কোম্পানীর সহিত চুক্তি অনুযায়ী তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিয়া এবং ভ্যাক্সিটার্ট সহ উচ্চ কর্মচারীদের প্রচুর অর্থ দিয়া তিনি তাহাদের সহিত অর্থের লেনদেনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিলেন।
(২) অতঃপর তিনি রাজকোষের আয়বৃদ্ধির জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, অভিজাতবর্গ ও জমিদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ জোর করিয়া আদায় করিতে লাগিলেন; কয়েকটি নূতন ‘আওয়াব’ বা অতিরিক্ত কর স্থাপন করিলেন।
(৩) সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাসনব্যাপারে যথাসম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপভাবে তিনি তাঁহার অর্থাভাব অনেকটা দূর করিতে সক্ষম হইলেন।
(৪) ইহার পর তিনি উদ্ধত, বিদ্রোহী, ইংরাজের সমর্থন-পুষ্ট জমিদারগণকে দমন করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিলেন। এইরূপভাবে তিনি শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন।
(৫) সামরিক দুর্বলতা দূর করিবার জন্য সাময়িক শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে নূতন করিয়া গঠন করিতে শুরু করিলেন; সৈন্যদলকে ইওরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন এবং কামান ও বন্দুক নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিলেন। ইংরাজদের প্রভাব হইতে দূরে থাকিবার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন; ইহাকে একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।
মীরকাশিম ইংরাজদের সহিত একটি বাদ-বিসম্বাদে জড়াইয়া পড়িতে যে ইচ্ছুক ছিলেন তাহা সমাধানের চেষ্টা; আর্থিক সঙ্কট শাসনক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন
নহে। কিন্তু দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া ইংরাজদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া থাকিবার মত হীন মনোবৃত্তি-সম্পন্ন নবাব তিনি ছিলেন না। তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে কোন সময়ে তাঁহাকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে হইতে পারে তাহা তিনি জানিতেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে সত্যই সে যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল।
‘ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকার পাইয়াছিল। বিনাশুল্কে আমদানি-রপ্তানির সুবিধার জন্য কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ ‘দস্তক’ বা ছাড়পত্র স্বাক্ষর করিবার অধিকারও পাইয়াছিল। তাঁহারা এই অধিকারের অপব্যবহার করিয়া অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্রে ‘দস্তক’ স্বাক্ষর করিয়া বিলি করিতে আরম্ভ করিল।
ফলে কোম্পানীর কর্মচারীগণ ও তাহাদের কৃপাপুষ্ট দেশীয় ব্যবসায়ীগণ বিনা শুল্কে ব্যবসা করিয়া প্রভূত লাভবান হইতে লাগিল। ইহাতে রাজকোষের অর্থাগম যেমন কম হইল দেশীয় ব্যবসায়ীগণও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। মীরকাশিম ইংরাজ গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিকার না হওয়াতে তিনি দেশীয় প্রজাদের উপর হইতেও শুল্ক উঠাইয়া দিলেন।
রাজকোষের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি দেশীয় ব্যবসায়ীগণের স্বার্থরক্ষা করার মত সাহস দেখাইলেন।
বক্সারের যুদ্ধ ও ফলাফল
কিন্তু ইংরাজদের স্বার্থে আঘাত লাগে বলিয়া এই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত পন্থা তাহাদের মনঃপূত হইল না। পাটনার ইংরাজ বাণিজ্য কুঠির এজেন্ট এলিস (Ellis) নবাবকে জব্দ করিবার জন্য অকস্মাৎ পাটনা শহর আক্রমণ করিলেন।
সুতরাং ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নবাব বাধ্য হইলেন। তিনি অবশ্য পাটনা পুনর্দখল করিয়া সেখান’হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিলেন; কিন্তু পরপর কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যায় গমন করিয়া নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট শাহ আলমের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনী পুনরায় ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হইলে মীরকাশিম পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।
এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। বাংলার শেষ স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নবারের পতন হইল। পলাতক অবস্থাতেই
১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সন্নিকটে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।
ফলাফল ও গুরুত্ব ঃ
বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রথমত, ইহার ফলে বাংলার শেষ পরাক্রান্ত নবাব মীরকাশিম সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং ইংরাজদের ক্রীড়নকরূপে মীরজাফর পুনরায় নবাব হইলেন।
দ্বিতীয়ত, অযোধ্যার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস পাইল এবং তাঁহার রাজ্যে কোম্পানীর প্রভাব বিস্তৃত হইল। তৃতীয়ত, বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইংরাজ কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি সুনিশ্চিত হইল। তাই ভারতবর্ষে ব্রিটিশশক্তি প্রতিষ্ঠার দিক দিয়া বিচার করিলে পলাশীর চাইতে বক্সারের যুদ্ধ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধই হয় নাই; কিন্তু বক্সারে ভারতীয় শক্তিদের তুলনায় ইংরাজদের সামরিক শক্তির উৎকর্ষ প্রমাণিত হইল। বক্সারে তাহাদের সাফল্য ছিল সত্যই প্রশংসনীয়। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজশক্তির সংকেত পাওয়া গিয়াছিল; আর বক্সারের যুদ্ধের পর তাহা সুনিশ্চিতভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর হইতে ইংরাজদিগকে এদেশে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আর যুদ্ধ করিতে হয় নাই।
অতঃপর তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য। এইজন্যই বলা হইয়া থাকে যে পলাশীর চাইতে বক্সারের যুদ্ধই গুরুত্বপূর্ণ।
কিন্তু ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুনিশ্চিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলায় রাজনীতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। সম্প্রতি অধ্যাপক পি.জে.মার্শাল এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে কলিকাতার উপর ইংরাজ কোম্পানীর আধিপত্য ও তাহাদের বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি রাজনৈতিক ক্ষমতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল— কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নাই।