দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন উত্তর বিষয়বস্তু নামকরণ বড় ও ছোট প্রশ্ন উত্তর
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন উত্তর
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
দেনাপাওনা গল্পের বিষয়বস্তু
কাহিনির সংক্ষিপ্তসার
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন উত্তর:■ রামসুন্দর মিত্র ছিলেন ছা-পোষা এক গৃহস্থ। তাঁর পাঁচ ছেলের পর একটি মাত্র আদরের কন্যা নিরুপমা। মস্ত এক রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলের সঙ্গে নিরুপমার বিবাহ স্থির হল। পাত্রপক্ষ দশহাজার টাকা বরপণ এবং বহু দানসামগ্রী দাবি করল। এমন পাত্র হাতছাড়া করা উচিত নয় ভেবে রামসুন্দর নিজের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা না করেই রাজি হয়ে গেলেন। —রাজি হলেন ঐ বরপণ দিয়ে কন্যার বিবাহ দিতে।
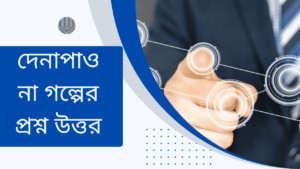
L) কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পণের ছয়-সাত হাজার টাকা সংগ্রহ করা গেল না। বিবাহ সভায় বিভ্রাট বাধল। পণের সম্পূর্ণ টাকা না-পেলে রায়বাহাদুর বর সভাস্থ করতে রাজি হলেন না। কিন্তু বর পিতার অবাধ্য হয়ে জানাল যে, সে ঐ কেনাবেচা,—দরদামের ব্যাপার বোঝে না; সে বিবাহ করতে এসেছে
, বিবাহ করবে। অতএব বিবাহ পর্ব সমাধা হল। → এই অসন্তোষের বিবাহ এবং তার পরিণাম অত্যন্ত বিষময় হয়ে উঠল নিরুপমা এবং তার বাবার পক্ষে। নিরুপমার শ্বশুরবাড়ি হয়ে গেল তার শরশয্যা; অপমান এবং লাঞ্ছনা হল তার প্রতিদিনের প্রাপ্য।
বাবাও পণের টাকা শোধ দিতে না-পারার জন্য কন্যার ওপর তাঁর স্বাভাবিক অধিকারটুকুও হারালেন। কন্যাকে শুধুমাত্র একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য বহু সাধ্যসাধনা করতে হয়, কখনো কখনো তাও ব্যর্থ হয়। রামসুন্দর তাঁর বসতবাড়িটি বিক্রি করে টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করলেন, কিন্তু ছেলেদের আপত্তিতে তাও সম্ভব হলো না।
অনেক চেষ্টা করে কিছু টাকা সংগ্রহ করে রামসুন্দর একবার বেহাইয়ের কাছে কিছুটা দেনা শোধ করতে গেলেন, কিন্তু রায়বাহাদুর ব্যঙ্গ করে বললেন, ছুঁচো মেরে তিনি হাত গন্ধ করবেন না। কাজেই পণের সব টাকাই চাই, নাহলে নিরুপমাকে তাঁরা পাঠাতে পারবেন না।
→ কিন্তু নিরুপমা বাপের বাড়ি আসবার জন্য বাবার কাছে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। রামসুন্দর কন্যাকে পুজোর সময় আনবার কঠিন প্রতিজ্ঞা করে অগত্যা বাড়িটিই গোপনে বিক্রি করে ফেললেন। কিন্তু টাকা দেবার দিন রায়বাহাদুরের বাড়িতে রামসুন্দরের বড় ছেলে হরমোহন তার ছেলেদের নিয়ে হাজির।
তাদের করুণ মুখ দেখে আর কাতর আবেদন শুনে নিরুপমা ব্যাকুল হয়ে বাবাকে বলল, তিনি যেন রায়বাহাদুরকে আর একটি পয়সাও না দেন; দিলে কন্যার মুখ আর তিনি দেখতে পাবেন না। বাধ্য হয়ে রামসুন্দরকে ফিরে আসতে হল।
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
→ এদিকে টাকা আনা সত্ত্বেও মেয়ে বাপকে টাকা দিতে দেয়নি, —এই সংবাদে নিরুপমার শ্বশুরশাশুড়ি হয়ে উঠলেন আরও নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। নিরুপমার ওপর লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।
নিরুপমাও নিজের জীবনের প্রতি একপ্রকার বীতশ্রদ্ধ হয়ে আহার নিদ্রায় কোন নিয়ম মেনে চলল না। শেষ পর্যন্ত সে কঠিন পীড়ায় হল আক্রান্ত। বাবা এবং ভাইদের সে একবার শেষ দেখা দেখতে চাইল, কিন্তু তার এই আবেদন শুধু বাপের বাড়ি যাবার ছল’ বলে শাশুড়ি তা নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।
→ যেদিন সন্ধ্যাবেলায় নিরুপমার অন্তিম শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হল, সেদিনই প্রথম ডাক্তার তাকে দেখতে এলেন এবং ডাক্তারের সেই শেষ আগমন। মৃত্যুর পর চন্দনকাঠের চিতায় নিরুপমাকে দাহ করা হল; শ্রাদ্ধের যে সমারোহ হল, তা ঐ অঞ্চলের লোকের কাছে অতীব এক বিস্ময়কর স্মৃতি হয়ে রইল।
→ এরপর নিরুপমার শাশুড়ি তাঁর ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রকে চিঠি দিলেন, তিনি এবার আর একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ করেছেন। ‘এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।’
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
♠ নামকরণ •
→ গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি যে কোন রচনার যে নামকরণ করা হয়, তার পিছনে থাকে রচনায় বর্ণিত কোন প্রধান ঘটনা বা কেন্দ্রীয় ভাব। প্রধান পুরুষ বা নারী চরিত্রের নামেও কাহিনির নামকরণ করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পের শিরোনামে কেন্দ্রীয় ভাবটিই প্রাধান্য পেয়েছে, কোনো চরিত্র নয়।
– দেনা’ ও পাওনার মধ্যে একটি আর্থিক সম্বন্ধ ব্যঞ্জিত। অধমর্ণ যে ঋণ করে, সেই ঋণকে বলে ‘দেনা’ ও উত্তমর্ণের প্রাপ্য ঋণের অর্থই হল তার ‘পাওনা’। এই দেনা ও পাওনা সমাজের
বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেখানে এদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থারে, সেখানেই শান্তি; ব্যতিক্রম ঘটলেই অশান্তি।
অর্থাৎ ঋণ গ্রহণ করে, যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলেই বিপত্তি। টাকাকড়ির লেনদেনের ক্ষেত্রে দেনাপাওনার হিসেবটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু বিবাহের মত একটি পবিত্র ও মধুর সামাজিক সম্পর্কের মাঝে দেনাপাওনা যখন দৌরাত্ম সৃষ্টি করে, তখন লজ্জা আর দুঃখের শেষ থাকে না।
→ রামসুন্দর মিত্র, রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার গিয়ে কীভাবে নিজে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন এবং শেষে মেয়েকেও হারালেন, তারই বেদনা-রূপ এক কাহিনি হল ‘দেনা-পাওনা’ গল্পের উপজীব্য। নিতান্ত স্বল্পবিত্ত রামসুন্দর মিত্র তাঁর আদরের কন্যা নিরুপমার সুখের জন্য তার বিবাহ দিয়েছিলেন ধনী রায়বাহাদুরের এক মাত্র পুত্রের সঙ্গে।
চুক্তি অনুসারে পণের দশহাজার টাকা পাত্রের পিতার কাছে তাঁর দেনা। এই দেনার প্রায় অর্ধেকটাও তিনি বিবাহের সময় বা পরে শোধ করতে পারলেন না। এই দেনা শোধ করতে না পারার জন্য তাঁর কন্যা শ্বশুরবাড়িতে যে শুধু স্নেহ, যত্ন, সম্মান পেল না, তাই নয়, তার শোচনীয় মৃত্যুও ত্বরান্বিত হল। অন্যদিকে এই পণের পাওনার টাকা না পেয়ে মানুষ যে কত নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হতে পারে, তা নিরুপমার শ্বশুর-শাশুড়ি দেখিয়ে দিলেন।
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
অথচ যে টাকার জন্য এই মৃত্যু ঘটানো হল, তার বহুগুণ টাকা তার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের সমারোহে ব্যয় করা হল! দরিদ্রের ওপর ধনীর এই নিষ্ঠুর প্রতিশোধ প্রবৃত্তি এবং শূন্যগর্ভ আভিজাত্যের ডঙ্কা নিনাদের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বহীনতার যে বাস্তব কুৎসিত চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, তা দেখে আমরা আজো বেদনায় অভিভূত হই। কিন্তু দুঃখ এই, এইবিবাহের দেনা-পাওনা মেটাতে দেনাপাওনা অর্থাৎ এই ‘পণপ্রথা’ আজো আমাদের সমাজে চলছে।
→ এই বিষময় প্রথার যূপকাষ্ঠে কত মেয়েই না আত্মবলি দিয়েছে ; কত নাটক, কত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এর বিরুদ্ধে,—কিন্তু এ প্রথার আজো শেষ নেই। দু’ একটি বিবেকবান প্রতিবাদী কণ্ঠ যে নেই, তা নয়, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত তুচ্ছ। নিরুপমার অকালমৃত্যু তাকে তার জীবনের দেনাপাওনার নিষ্ঠুর জটিলতা থেকে মুক্তি দিয়েছে।
এই শ্লেষাত্মক অথচ করুণ ব্যঞ্জনাটি গল্পের বাতাবরণটিকে শোকবহ করে তুলেছে। আবার অন্তিমের বিশহাজার টাকার হাতে হাতে আদায়ের মধ্যে ইংগিত রয়েছে আর এক দেনাপাওনা শুরু। তাই গল্পের শিরোনাম এই অর্থে বিশেষ তাৎপর্যবহ এবং ব্যঞ্জনাময়।
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
দেনাপাওনা গল্পের বড় প্রশ্ন উত্তর
রচনাধর্মী, আলোচনামূলক, ব্যাখ্যামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
প্রশ্ন : । রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে তৎকালীন সমাজজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দাও। গল্পটির আবেদন আজকের জীবনেও কতখানি তা বিচার কর।
• উত্তর : মানুষ সামাজিক জীব। সেই সামাজিক মানুষের জীবন তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। কোন লেখকই তাঁর সমাজ এবং যুগজীবনকে অস্বীকার করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। সমাজসমস্যা যে গল্পগুলির মুখ্য উপজীব্য, ‘দেনাপাওনা’ হল তাদের অন্যতম।
→’দেনাপাওনা’ গল্পে আমরা যে-সমাজকে পাই, তার একদিকে রয়েছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র রামসুন্দর মিত্র। তিনি তাঁর অভাব-অনটনে জর্জরিত, অন্যদিকে আছেন অতি উচ্চবিত্ত ধনী রায়বাহাদুর। অর্থ কৌলিন্যই ছিল ওই রায়বাহাদুরদের কাছে মনুষ্যত্ব নির্ণায়ক মাপকাঠি। আভিজাত্যের অহংকার এবং প্রতিপত্তির জোরে এঁরা সর্বপ্রকার মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে অতিমাত্রায় ছিলেন নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন।
→ নিজে দরিদ্র হয়ে রায়বাহাদুরের মত বিত্তবান ঘরের পুত্রের সঙ্গে কন্যা নিরুপমার বিবাহ দেওয়াটা রামসুন্দরের ঠিক হয়নি। কিন্তু স্নেহবৎসল পিতা তাঁর কন্যার জন্য সাধ্যমত শ্বশুরবাড়ির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে গিয়েছিলেন, পরিণাম চিন্তা করেন নি; এটি রামসুন্দরের একার দোষ নয়, বরং সামাজিক প্রথারই দোষ।
তিনি পণের টাকা সম্পূর্ণ দিতে পারলেন না। রায়বাহাদুর বিবাহ ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ছেলে তা চায়নি। সে পিতার বিরোধী হয়ে বিবাহ করল। নিরুপমার প্রতি তার শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতিহিংসার এটাও একটা কারণ।
→ বিবাহের পর নিরুপমাকে একবারও বাপের বাড়ি আসতে দেওয়া হয়নি। সেবার পুজোর সময় তাকে আনবার জন্য বাবা রামসুন্দর মরিয়া হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে পণের বাকি কিছু টাকা সংগ্রহ করে রামসুন্দর একবার বেহাইকে দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চান না বলে সেই সামান্য টাকা রায়বাহাদুর স্পর্শ করেননি, ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং রামসুন্দরকে অপমান করেছিলেন।
শেষে গোপনে বসতবাড়িটি বিক্রি করে সব টাকা নিয়ে বড় আশা করে রামসুন্দর নিরুপমাকে আনতে গেলেন। কিন্তু নিরুপমা টাকা সংগ্রহের উপায় জানতে পেরে বাবাকে বলল, –‘তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।’
→ এরপর নিরুপমার পক্ষে তার শ্বশুরবাড়ি হয়ে উঠল শরশয্যা। লাঞ্ছনার বোঝা দিনে দিনে বাড়তে থাকল এবং শেষে তার শোচনীয় মৃত্যু ঘটল। বীভৎস পণপ্রথার শিকার হয়ে সে একরকম স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিল এবং আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে সে প্রতিবাদ জানিয়ে গেল পণপ্রথার বিরুদ্ধে, বিশেষ ভাবে নারীত্বের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে।
নিরুপমার এই প্রতিবাদ ও বেদনা রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই শ্লেষ চরম হয়ে উঠেছে গল্পের অন্তিম অংশে, যেখানে রায়বাহাদুর তাঁর ছেলের পুনবিবাহের ব্যবস্থা করে ছেলেকে জানিয়েছেন। ‘এবার বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।’
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
→ গল্পের আদ্যন্ত প্রতিবাদমুখর। এই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে নিরুপমার মধ্যে, তার স্বামীর মধ্যে। নিরুপমা বলেছে ‘আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম?’ নিরুপমার স্বামী পিতার অবাধ্য হয়ে বলেছে ‘কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।’
যুবসমাজের এই প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ‘দেনাপাওনা’য় এই প্রতিবাদকে কবি জয়যুক্ত করতে পারেননি; এ প্রতিবাদে জয়ী হয়েছে পরবর্তীকালে রচিত ‘যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ’ গল্পে। —এখানে নয়।
বর্তমান সমাজে বিবাহ ব্যাপারে যে মানবিক সচেতনতা যুবকদের মধ্যে দেখা যায়, তা কম হলেও, তার মূলে এইসব গল্পের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। তাই ‘দেনাপাওনা’র সামাজিক আবেদন আমাদের জীবনে দিনে দিনে অধিকতর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।
কারণ সমস্যাগুলি ব্যক্তিগত হয়েও কিন্তু সামাজিক। সামাজিক এ সমস্যা সেদিনের যতখানি সমস্যা, আজকেরও ততখানি সমস্যা। তাই গল্পটির আবেদন আজকের জীবনেও অনস্বীকার্য। এই গল্পের আবেদন আজও রয়েছে।
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
প্রশ্ন : । রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে নিরুপমার জীবনের করুণ পরিণতির জন্য কে বা কারা দায়ী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
অথবা, রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ ছোটগল্পের নায়িকা নিরুপমার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে বা কারা? কীভাবে তাদের দায়ী করা যায়? তোমার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পের নায়িকা হল নিরুপমা। তার জন্ম, নামকরণ, বিবাহ এবং মৃত্যু—অর্থাৎ সমগ্র জীবন নিয়ে এই গল্প আবর্তিত হয়েছে। গল্পের শেষে তার জীবনের যে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছে, তা হত্যা নয়, আত্মহত্যা নয়, রোগাক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যু। তবে এই রোগের পেছনে যাদের পরোক্ষ অবদান এবং সামাজিক ও পারিবারিক কার্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে, গল্পটি বিশ্লেষণ করলে তাদের আমরা চিনতে পারি।
→ নিরুপমার মৃত্যুর জন্য অবশ্যই প্রধানত দায়ী আমাদের সমাজের জঘন্য পণপ্রথা ৷ পণ দেওয়ানেওয়ার প্রথা না থাকলে, দরিদ্র রামসুন্দর তাঁর সাধ্যাতীত দাম দিয়ে ধনী রায়বাহাদুরের পুত্রকে পাত্র হিসেবে কিনতে সাহস পেতেন না; অপরপক্ষে রায়বাহাদুরের মত অর্থলোলুপ ধনীরাও শুধুমাত্র অর্থের লোভে অসম আত্মীয়তায় রাজি হতেন না।
এঁদের কাছে ছেলের বিবাহ যেন একটা ব্যবসা। তাই দশ হাজার টাকার চুক্তিতে গোলোমালে কিছু লোকসান হলে, তার ক্ষতিপূরণ করবার জন্য পুনরায় বিশ হাজারের চুক্তি হয়।
পণের টাকাকে কেন্দ্র করে রায়বাহাদুর বিরূপ হয়েছেন বৈবাহিকের প্রতি; তিনি আত্মীয়কে কোন স্বীকৃতি দেননি এবং সম্মান না দিয়ে তাঁকে পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন। রায়বাহাদুরের স্ত্রীর ব্যবহার আরও নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন। তিনি পুত্রবধূকে কোনোদিন কন্যার মত দেখেন নি এবং ভাবতে পারেননি।
পণের পুরা টাকা না দিতে পারার জন্য বধূকে তিনি পুরো মর্যাদা তো দেননি, এবং ন্যূনতম মানবিক বোধটুকুও তাঁর ব্যবহারে একবারের জন্যও দেখা যায় না। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নিরুপমাকে স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। যে বধূকে ক্ষুধার অন্ন এবং রোগের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, মৃত্যুর পরে মহা সমারোহে তারই অন্ত্যেষ্টি করা হয়েছে, শ্রাদ্ধ করা হয়েছে।
এঁদের কাছে বিবাহে প্রেম নেই, শান্তি নেই; আছে শুধু পণ নেওয়া তাই জঘন্য পণপ্রথা এবং তার দক্ষ ধারক ও বাহক রূপে নিরুপমার শ্বশুর-শাশুড়িকে তার মৃত্যুর জন্য প্রায় সবটাই দায়ী করা যায়।
→ নিরুপমার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকেও একেবারে নিরপরাধ বলা যায় না। সে তার অর্থলোভী পিতা এবং মাতাকে নিশ্চয়ই চিনত। কাজেই পিতার আপত্তি সত্ত্বেও উদারতা দেখিয়ে বিবাহ করা তার ঠিক হয়নি। আর যদি-বা করল, বিবাহের পরে কর্মস্থানে গিয়ে তার দীর্ঘদিন চুপ করে থাকা যথার্থ হয়নি। ——স্বামীটি এখানে ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষ।
→ নিরুপমার শ্বশুর-শাশুড়ি এবং স্বামীর মত রায় বাহাদুরের পরিবারের পরিচারক ও পরিচারিকারাও তার প্রতিকূল অবস্থাকে অনেকটা জটিল করে তুলেছে, স্নেহ সহৃদয়তা তাদেরও তেমন দেখা যায় নি। কারণ বসতবাড়ি বিক্রি করে পণের সব টাকা এনেও নিরুপমার নিষেধে রামসুন্দর টাকা না দিয়ে ফিরে গেলেন,— এ ব্যাপারটা ‘দ্বারলগ্নকর্ণী’ কোন দাসী না জানালে
নিরুপমার শ্বশুর-শাশুড়ি কিছুই জানতে পারতেন না। তাহলে শ্বশুরবাড়িও নিরুপমার পক্ষে অতখানি শরশয্যা হয়ে উঠত না। তাই নিরুপমার মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে ঐ পরিবারের দাসীচাকরদের দায়িত্বও কম নয়।
→ শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে নিরুপমার বাপের বাড়ির দায়িত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। এদিক থেকে প্রথমেই তার বাবা রামসুন্দর অপরাধী। স্নেহবৎসল হতভাগ্য পিতা কন্যার জন্য দশ হাজার টাকার বিনিময়ে সুখ সৌভাগ্য কিনতে চেয়েছিলেন। যথাসর্বশ্বের বিনিময়ে তিনি কন্যাকে সুখী করতে চেয়েছেন, কিন্তু পরিবারের আর কারো কথা তিনি ওইভাবে একবারও চিন্তা করেননি। রবীন্দ্রনাথ গল্পের প্রথমেই তাই তাঁর অবিবেচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই অবিবেচনা এবং অপরিণামদর্শিতা নিরুপমার দুঃখের জন্য অনেকটাই দায়ী।
→ এছাড়া এই গল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রামসুন্দরের পুত্ররাও কেউ পিতাকে বিপন্মুক্ত করবার জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করেনি। তারা রামসুন্দরের কাজে বাধা দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নেয়নি। শেষ বারে জ্যেষ্ঠ পুত্র হরমোহন যদি রায়বাহাদুরের বাড়িতে গিয়ে নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা না করত, তবে নিরুপমা প্রতিবাদী হয়ে তার বাবাকে টাকা দিতে নিষেধ করত না। কাজেই হরমোহনের আচরণ যে নিরুপমার শোচনীয় পরিণামকে অনেকটা ত্বরান্বিত করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।
→ অবশেষে বলা যায়, নিরুপমার মৃত্যুর জন্য নিরুপমা নিজেও কম দায়ী নয়। সে পাঁচ ভাইয়ের কোলে একটি আদরের বোন; স্বভাবতই সে কিছু অভিমানী। বাবা এবং ভাইদের মুখ চেয়ে শ্বশুরবাড়ির অপমান, গঞ্জনা সে নীরবেই সহ্য করেছে। শেষে আঘাতের তীব্রতায় ধীরে ধীরে তার ভেতর আত্মাভিমান এবং মর্যাদাবোধ জেগে উঠেছে।
সে যে ঝি-চাকরদেরও করুণার পাত্রী, এই বোধ তাকে ধীরে ধীরে আত্মহননের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই মানসিক অভিঘাত তার মৃত্যুর অন্যতম কারণ। —মানসিক দিক থেকে নিরুপমা যদি দৃঢ় হতে পারত, তা হলে ঐ মর্মান্তিক পরিণতি তার হত না।
→ তাই সার্বিক বিচারে বলা যায়, কোন একক ব্যক্তি বা কোনো একটি ঘটনা নিরুপমার মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়, সামগ্রিকভাবে প্রায় সকলেই দায়ী। তবে পণের দেনাপাওনার ব্যাপারটাকে কোনো রকমেই গৌণ করা চলে না। এটাই মুখ্য। এই পণপ্রথাকে কেন্দ্র করেই গল্পের সমস্ত জটিলতা।
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
প্রশ্ন : । রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্প অবলম্বনে নিরুপমার চরিত্র বর্ণনা কর।
উত্তর : নিরুপমা রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পের নায়িকা। তার দুর্ভাগ্যময় জীবন কাহিনিই এ গল্পের প্রধান কথাবস্তু। নিরুপমাকে কেন্দ্র করেই গল্পের সমস্ত ঘটনা আবর্তিত। আধুনিক সাহিত্যের সাফল্য হল সজীব চরিত্রচিত্রণে। যে কোন ব্যক্তির কর্ম ও কথার মধ্যে দিয়ে তার চরিত্র গড়ে ওঠে। দেনাপাওনা গল্পেও স্বল্প পরিসরের মধ্যে চরিত্রগুলি নিজেদের দোষগুণসহ সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে।
→ নিরুপমা নিম্নমধ্যবিত্ত এক বাঙালি গৃহস্থের কন্যা। এই কন্যা ধনী নয়, কিন্তু রূপের কৌলীন্যে ধনী রায়বাহাদুরের ঘরের বধূ হবার যোগ্যতা তার ছিল। নিরুপমা নামটি আদরের দেওয়া, কিন্তু নামের মধ্যে অর সত্য পরিচয়ও প্রচ্ছন্ন। তার রূপ যেমন অতুলনীয়, তেমনি গুণেরও কোন উপমা ছিল না।
রায়বাহাদুর শুধু যে দশ হাজার টাকা পণের লোভেই তাকে পুত্রবধূ করতে চেয়েছিলেন তা মনে হয় না, তিনি পাত্রীর রূপে বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ি বিদ্বেষবশে বধূর এই রূপের কথা মুখে স্বীকার না করলেও প্রতিবেশীরা কেউ কেউ বলেছে, ‘আহা, কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।’
→ নিরুপমা স্বভাবে শান্ত, ধৈর্যশীলা মেয়ে। বিবাহের রাত্রিতে যখন পণের টাকা নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়েছে এবং বিবাহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছে, তখন শান্তভাবে সে সমস্ত উল্লেখ দমন করেছে, ধৈর্য ধরে মধুর মুহূর্তের প্রতীক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘এই গুরুতর বিপদে যে মূল কারণ, সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে → নিরুপমার ধৈর্য যে কী অসীম ও অটুট, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তার শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনাগঞ্জনা কণ্টকিত দিনগুলির মধ্যে দেখিয়েছেন। গৃহস্বামী থেকে পরিচারিকা পর্যন্ত সকলের কাছ থেকেই সে পেয়েছে মানসিক নির্যাতন, কিন্তু তার অন্তরের দুঃসহ বেদনা কোথাও অশালীন আচরণ বা অভদ্র ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেনি।
→ এই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে আরও সুন্দর করেছে নিরুপমার অপার মমত্ববোধ। বাবা এবং ভাইদের মুখ চেয়েই সে শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেছে, তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য একবার সে বাপের বাড়িও যেতে চেয়েছিল। শাশুড়ির তীব্র ভর্ৎসনা মুখ বুজে সহ্য করে সে সবিনয়ে বলেছে, ‘বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।’
→ এই মমতা ও মর্যাদাবোধের আর-এক আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে স্বামীর প্রতি নিরুপমার নীরব ভালবাসার মধ্যে। তাকে শুধুমাত্র বিবাহ করা ছাড়া তার স্বামী তার জন্য তো আর কিছু করতে আসেনি, বরং তার অবিবেচনা ও নীরব ঔদাসীন্য নিরুপমার মৃত্যুর পথকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে। এজন্য নিরুপমা কিন্তু কোনদিন অভিযোগ জানায়নি। উপরন্তু রামসুন্দর পণের টাকা শোধ দিতে এলে সে বলেছে, “…আমার স্বামী তো এ-টাকা চান না।’ —স্বামীর প্রতি তার এই শ্রদ্ধাবোধ, তাকে আরো সুষমামন্ডিত করেছে।
→ এ পর্যন্ত নিরুপমার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাকে একজন চিরন্তন বাঙালি নারী বলেই মনে হয় । এ নারী শান্তি চায়, বেদনায় বুক ফেটে যায়, কিন্তু মুখ ফুটে কোন প্রতিবাদের বাণী উচ্চারণ করে না। নিরুপমা নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা একবারের জন্য চিন্তা করেনি ; বাবা এবং ভাইদের শোচনীয় দুর্দশায় সে বেদনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। বাবার দুরবস্থা, দাদার বিলাপ ও তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে, সমস্ত অনিষ্টের জন্য নিজেকেই সে শেষ পর্যন্ত অপরাধী মনে করেছে। অন্য কারোকে সে দোষ দেয়নি, এই সঙ্গে তার মর্যাদাবোধও প্রশংসনীয়। সে তার বাবাকে পণের টাকা দিতে নিষেধ করে বলেছে, ‘তোমার মেয়ের কী কোনো মর্যাদা নেই । আমি কী কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ-টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।’
→ যদিও এ প্রতিবাদ সুফলপ্রসূ হয়নি, তবু নিরুপমা সমস্ত লাঞ্ছিত নারীজাতির হয়ে এখানে প্রতিবাদ মুখর। এই প্রতিবাদের জন্যই নিরুপমা নবযুগের ইঙ্গিতবাহী এক চরিত্র হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।
প্রশ্ন : । “এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল।”—এখানে কোন্ দুর্ঘটনার কথা বলা হয়েছে? একে দুর্ঘটনা বলার কারণ কী? অন্তঃপুরে কান্না পড়ে গেল কেন? এই দুর্ঘটনার যে মূল কারণ সে তখন কী করছিল? কান্না থামল কী করে?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে রায়বাহাদুরের ডেপুটি পুত্রের সঙ্গে রামসুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমার বিবাহে বরপণ ধার্য হয়েছিল নগদ দশ হাজার টাকা। বিয়ের রাতে সেই পণের পুরা টাকা হাতে না পেয়ে রায়বাহাদুর বর সভাস্থ করতে সম্মত হলেন না। —এটাই হল এই দুর্ঘটনা।
→ এটিকে দুর্ঘটনা বলবার কারণ হল, বর সভাস্থ না হওয়া মানে বিবাহ বাতিল। এই বিবাহ বন্ধ হয়ে গেলে পাত্রপক্ষের খুব সামান্য হয়তো ক্ষতি হবে, কিন্তু কন্যাপক্ষের ক্ষতি অনেক। প্রথমত দরিদ্র কন্যাকর্তা যে ব্যয়বহুল আয়োজন করেছেন, তা নষ্ট হবে এবং তার পুনরায়োজন করা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। আর সবার ওপরে বড় ক্ষতি হল, ভ্রষ্টলগ্না কন্যাকে কেউ পরে বিবাহ করতে চাইবে না।
হবু পাত্রপক্ষ ভাববে, হয় কন্যা অপয়া, নতুবা মেয়ের চরিত্রে কোন দোষ আছে। → অন্তঃপুরে শুধুই মেয়েরা থাকেন। বর সভাস্থ না হলে বিবাহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা চিন্তা করেই অন্তঃপুরে মেয়েদের ভেতর কান্নার রোল পড়ে গেল। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় পুরুষরা যতটা সংযত থাকতে পারেন, মেয়েরা তা পারেন না। তাই তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন।
→ এই দুর্ঘটনার কেন্দ্রস্থানীয় চরিত্র হল নিরুপমা। কলরোল এবং ক্রন্দনের মধ্যে সে তখন বিবাহের চেলি পরে, গহনা পরে, কপালে চন্দন লিপ্ত হয়ে চুপ করে বসেছিল। হয়তো ভাবী শ্বশুরের সম্পর্কে ভক্তি ও অনুরাগের পরিবর্তে তার মনে শ্বশুরালয়ের প্রতি অজানা শঙ্কা ও সংশয় উঁকি মারছিল।
→ কান্না থামল স্বয়ং বরের হস্তক্ষেপে। সে হঠাৎ পিতার অবাধ্য হয়ে বলল, ‘কেনাবেচা-দরদামের কথা বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।’ এতেই সাময়িকভাবে বিপদ কাটল, বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।
প্রশ্ন : । “ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল।”—বক্তা কে? কী সুবিধা হয়েছিল? একে কী প্রকৃত সুবিধা বলা যায়? তোমার নিজস্ব যুক্তি দিয়ে বোঝাও।
উত্তর : ‘দেনাপাওনা’ গল্পে এই অংশের বক্তা হলেন স্বয়ং লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
→ রায়বাহাদুরের ডেপুটি পুত্রের সঙ্গে রামসুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমার বিবাহে বরপণ ধার্য হয়েছিল নগদ দশ হাজার টাকা। সেই সম্পূর্ণ টাকাটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত বিবাহের রাতে রায়বাহাদুর বর সভাস্থ করতে চাইলেন না। তখন বর স্বয়ং পিতার অবাধ্য হয়ে বললে, সে কেনাবেচা,—দরদামের কথা বোঝে না, বিবাহ করতে এসেছে, বিবাহ করবে। পাত্রের এই সাহসী সিদ্ধান্তকেই লেখক সুবিধা বলেছেন।
→ পাত্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে যে-বিবাহ ভেঙে যেতে বসেছিল, তা ভাঙল না। কাজেই এটাকে একটা সুবিধা বলা যায়। কিন্তু গল্পের পরিণাম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ বিবাহ না হলেই বরং ভালো হত। রায়বাহাদুর পণের পুরা টাকা হাতে পেলেন না; উপরন্তু পুত্র পিতার অবাধ্য হয়ে বিবাহ করল।
এতে পাত্রপক্ষের সমস্ত অসন্তোষ ও আক্রোশ গিয়ে পড়ল নিরুপমা এবং তার বাবার ওপর। যত্ন ও আদরের পরিবর্তে খোঁটা ও লাঞ্ছনা হতে থাকল নববধূর নিত্য পাওনা। দিনে দিনে নিরুপমার পক্ষে তার শ্বশুরবাড়ি হয়ে উঠল শরশয্যা। এর ওপর পরে দেখা গেল বেহাই বাড়িতে পিতা রামসুন্দরের চরম অপমান এবং কন্যার সঙ্গে প্রায় সম্পর্কচ্ছেদ।
নিরুপমা এই কঠোর মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে অভিমানে আত্মহননের পথ বেছে নিল। আহার নিদ্রার অনিয়মে সে সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং শেষে তার মৃত্যু হল। নিরুপমার প্রবাসী ডেপুটি স্বামী এর কিছুই খোঁজ রাখল না।
→ তাই মনে হয়, পাত্রের উক্ত সিদ্ধান্ত তখন ‘সুবিধাজনক’ মনে হলেও,পরিণামে মারাত্মক হয়েছিল। ঐ অসম বিবাহ না হলে বোধহয় নিরুপমার অমন শোচনীয় অকালমৃত্যু হত না।
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
প্রশ্ন : । “কেনাবেচা–দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।”—উদ্ধৃতাংশটির বক্তা কে? উক্তিটির প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। উক্তিটি বক্তার চরিত্রের কোন্ দিকটিকে উদ্ভাসিত করেছে?
• উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে আলোচ্য অংশের বক্তা হল রায়বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিস্টেট পুত্র।
→ রায়বাহাদুরের পুত্রের সঙ্গে রামসুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমার বিবাহ স্থির হয় এবং ঐ বিবাহে বরপণ ধার্য হয়েছিল নগদ দশ হাজার টাকা। সেই পণের সম্পূর্ণ টাকা বিয়ের রাতে হাতে না এলে রায়বাহাদুর বর সভাস্থ করতে চাইলেন না। তার ফলে চারিদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল এবং বিবাহ ভেঙে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল।
রামসুন্দর রায়বাহাদুরের হাতে পায়ে ধরতে লাগলেন। লগ্নভ্রষ্টা কন্যার দুর্বিষহ পরিণামের কথা চিন্তা করে অন্তঃপুরে মেয়েরা কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এইসব মিলিয়ে পাত্রের মনে একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শুরু হল এবং তার ফলেই সে পিতৃবিরোধী এক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই উক্তি করেছিল।
→ এই উক্তির মধ্যে দিয়ে বক্তার প্রগতিশীল মানবিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক। তাই পণপ্রথার বিরোধিতা তার কাছে প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ যুবক পণপ্রথার বিরুদ্ধে মুখে বড় বড় বক্তৃতা দিলেও, কার্যকালে সুবোধ বালকের মত পিতা-মাতার আনুগত্য মেনে পণপ্রথায় সায় দেয়।
কিন্তু আমাদের রায়বাহাদুর পুত্র তা করেনি। সে পিতার আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। পরপীড়ন করে অন্যায়ভাবে পণ নেওয়াকে সে সমর্থন করেনি। তাই নীতিশিক্ষা এবং শাস্ত্রশিক্ষার অভাব নিয়ে সভাস্থ প্রবীণরা পাত্র সম্পর্কে যতই বিরূপ মন্তব্য করুন না কেন, প্রতিবাদী পাত্রটি সকলের সহৃদয় সমর্থন লাভ করেছে।
কিন্তু এই প্রতিবাদী চরিত্রটিকে কবি শেষ পর্যন্ত সক্রিয় রেখে গল্পের উপসংহার টানেন নি; বোধ হয় কলঙ্কময় পণপ্রথা এবং নিরুপমার শোচনীয় জীবন-পরিণাম দেখানোর উদ্দেশ্যেই ঐ চরিত্রটিকে আড়ালে রেখে খর্ব করা হয়েছে।
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
প্রশ্ন : । “বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।”—কার বিবাহের কথা বলা হয়েছে? এ রকম বিষণ্ন এবং নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হবার পিছনে কারণ হিসাবে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা লেখ।
অথবা, কার বিবাহ ? তা বিষণ্ণ ও নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হবার কারণটি লেখ।
উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে রায়বাহাদুরের একমাত্র ডেপুটি মাজিস্ট্রেট পুত্রের
সঙ্গে রামসুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমার বিবাহের কথা এখানে বলা হয়েছে। । রামসুন্দর মিত্র নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পাঁচ ছেলের পর তাঁর একটি মাত্র কন্যা। ঐ কন্যার আদরের নাম, নিরুপমা। নিরুপমা বিবাহ যোগ্যা হলে তার বিবাহের জন্য অনেক সন্ধান করে অবশেষে এক ধনী রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে রামসুন্দর তাঁর কন্যার বিবাহ স্থির করলেন।
পাত্রপক্ষ দশ হাজার টাকা পণের সঙ্গে দান সামগ্রীও দাবি করলেন। রামসুন্দর নিজের সাধ্য ও সঙ্গতির কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করে, তাতেই সম্মতি দিলেন। কারণ পাত্রটি তাঁর মতে হাতছাড়া করা অনুচিত।
→ সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে, বিক্রি করে এবং বহু চেষ্টা করেও রামসুন্দর পণের ছয়-সাত হাজার টাকা কিছুতেই জোগাড় করতে পারলেন না।
→ এদিকে বিবাহের দিন উপস্থিত। যে লোকটি অনেক চড়া সুদে বাকি টাকাটা ধার দিতে চেয়েছিল, সেও সময়কালে এসে পৌঁছালো না। কাজেই বিবাহ বিভ্রাট দেখা দিল। রামসুন্দর রায়বাহাদুরের হাতে পায়ে ধরে এবং মিনতি করে বললেন, শুভকার্যের পর তিনি সব টাকা শোধ করে দেবেন। কিন্তু রায়বাহাদুর টাকা না-নিয়ে বিবাহ বাসরে বর সভাস্থ করতে সম্মত হলেন না। এতে অন্তঃপুরেও কান্নার রোল শোনা গেল।
→ তখন সমস্ত পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করে এবং সম্মান বাঁচাতে স্বয়ং বর তার পিতার অবাধ্য হয়ে উঠল। সে বাবাকে বললে, ‘কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, আমি বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।’
→ এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে উপস্থিত সকলেই বেশ বিস্মিত হলেন। সভাস্থ প্রবীণরা তরুণ যুবাদের শাস্ত্রশিক্ষা ও নীতিশিক্ষার অভাব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর মন্তব্য করলেন। রায়বাহাদুর মহাশয়ও স্বীয় পুত্রের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার কুফল প্রত্যক্ষ করে সাময়িকভাবে কিছুটা উত্তেজিত হলেন।
কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল বিবেচনা করে, একটু পরেই তিনি থেমে গেলেন। ক্ষোভে ও অপমানে তাঁর মন ভরে গেল। তাই বিবাহ সম্পন্ন হল ঠিকই, কিন্তু তা বিষণ্ন ও নিরানন্দভাবে।
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
প্রশ্ন “বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত।”—কোন্ গল্পের অংশ এটি? মেয়েটি কে? ‘পুরা দাম’ কথাটির অর্থ কি ? কোন্ ঘটনার জন্য লেখক এ রকম উক্তি করেছেন? মেয়েটি ‘পুরা যত্নে’র বদলে কোন্ ধরনের ব্যবহার পেয়েছিল তা লেখ।
● উত্তর:আলোচ্য বাক্যটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘দেনাপাওনা’ ছোট গল্পের অংশ।
→ এখানে ‘মেয়েটি’ বলতে ঐ গল্পের নায়িকা নিরুপমাকে বোঝানো হয়েছে। নিরুপমা রামসুন্দর মিত্রের একমাত্র কন্যা এবং ধনী রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রবধূ।
→ ‘পুরা দাম’ বলতে সম্পূর্ণ মূল্যকে বোঝায়। খণ্ডমূল্য নয়। এখানে নিরুপমার বিবাহের বরপণের দশ হাজার টাকাকে বোঝানো হয়েছে। —এই টাকাটাই পুরাদাম।
[] দরিদ্র রামসুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমার বিবাহ হয়েছিল ধনী রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু দশ হাজার টাকা বরপণ দিতে সম্মত হয়েও রামসুন্দর সব টাকা বিবাহের রাতে শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারলেন না। পাত্র পিতার আপত্তি সত্ত্বেও বিবাহ করল, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে বধূ নিরুপমার ভাগ্যে সুখ-সৌভাগ্যের পরিবর্তে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা জুটল প্রতিদিনের পাওনা হিসাবে। শ্বশুরবাড়ির নিষ্ঠুর ব্যবহার যেন প্রতিনিয়ত বুঝিয়ে দিতে লাগল যে, পণের পুরা টাকা দিতে পারলে সে পুরা যত্ন পেত। দেনা পরিশোধে পিতার অক্ষমতাই কন্যার সুখশান্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।
→ নিরুপমা তার শ্বশুরবাড়িতে যে ব্যবহার পেল, তা এক কথায় অত্যন্ত অমানবিক, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। দুটি অসম অবস্থার পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হল, কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোন উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠল না। স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি, সম্মান তো কিছুই নিরুপমা পেল না, উপরন্তু এদিকে রামসুন্দর তাঁর কন্যার ওপর স্বাভাবিক অধিকারটুকুও হারালেন।
কন্যাকে একবার শুধু চোখের দেখা দেখবার জন্যও বহু সাধ্য-সাধনা তাঁকে করতে হত, কখনো সেই সাধ্য সাধনাও ব্যর্থ হত। অনেক চেষ্টার পর কিছু টাকা যোগাড় করে একদিন তিনি বেহাইয়ের ঋণ শোধ করতে গেলেন, কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চান না বলে এই সামান্য টাকা রায়বাহাদুর স্পর্শ করলেন না; উপরন্তু তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে অপমানিত করলেন। পণের বাকি টাকা সবটা নাপেলে নিরুপমাকে যে বাপের বাড়ি পাঠানো হবে না, তা জানিয়ে দেওয়া হল।
→ কিন্তু নিরুপমা পিতৃগৃহে আসবার জন্য বাবাকে মিনতি করতে লাগল। রামসুন্দরের মনও ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি কন্যাকে পুজোর সময় গৃহে আনবার কঠিন প্রতিজ্ঞা করে, নিরুপায় হয়ে শেষ
পর্যন্ত গোপনে বসতবাড়িটি বিক্রি করে দিলেন। কিন্তু টাকা দেবার দিন রায়বাহাদুরের বাড়িতে রামসুন্দরের বড় ছেলে হরমোহন তার ছেলেদের নিয়ে হাজির হল। তাদের করুণ মুখ দেখে এবং কাতর আবেদন শুনে হঠাৎ নিরুপমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল; সে তার বাবাকে বলল, তিনি যেন রায়বাহাদুরকে আর একটি পয়সাও না দেন; দিলে কন্যার মুখ তিনি আর দেখতে পাবেন না।
অগত্যা রামসুন্দরকে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হল। → এদিকে ওই টাকা দেবার জন্য আনা সত্ত্বেও মেয়ে বাবাকে টাকা দিতে দেয়নি,—এ সংবাদে নিরুপমার শ্বশুর-শাশুড়ি বধূর ওপর হয়ে উঠলেন আরও ক্ষিপ্ত, আরো নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর। নিরুপমার
পক্ষে শ্বশুরবাড়ি হয়ে উঠল শরশয্যা। উঠতে বসতে তার কপালে জুটতে থাকল খোঁটা আর গঞ্জনা। বাপ পুরা দাম না-দেওয়ার অজুহাতে মেয়ের পুরা যত্ন তো বন্ধই হয়েছিল, এখন নিরুপমার খাবার দিতেও দাসদাসীরা প্রায়ই ভুল করতে লাগল। নিজেকে দাসদাসীদের কৃপার পাত্রী ভেবে নিরুপমাও আর তাদের খাবারের কথা স্মরণ করিয়ে দিত না। এই অনাদরের খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে শাশুড়ি তাকে ব্যঙ্গ করে বলতেন, নবাবের বাড়ির মেয়ের গরিবের বাড়ির অন্ন রুচবে কেন!
→ এমনি করে নিজের জীবনের প্রতি ভীষণভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল নিরুপমা। তিলে তিলে সে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথেই এগিয়ে গেল। যেদিন সন্ধ্যায় অসুস্থ নিরুপমার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হল, সেদিনই প্রথম তাকে ডাক্তার দেখানো হল এবং সেদিনই শেষ। মৃত্যুর পর চন্দনকাঠের চিতায় খুব ঘটা করে নিরুপমাকে দাহ করা হল; শ্রাদ্ধও হল বিরাট সমারোহে। না হলে, জমিদার রায় বাহাদুরের বাড়ির সম্মান রক্ষা হয় কেমন করে?
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন
প্রশ্ন ” “এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।”—এখানে কোন কণ্ঠ বলা হয়েছে? কে টাকা দিতে চেয়েছিলেন? টাকা দিয়ে অপমান করা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে? এই উক্তির মধ্যে বক্তার কোন্ চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে দরিদ্র রামসুন্দর মিত্র তাঁর কন্যা নিরুপমার বিবাহ দিয়েছিলেন ধনী রায়বাহাদুরের পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু বরপণের দশ হাজার টাকার সবটা তিনি পাত্রপক্ষকে বিবাহের সময় দিতে পারেননি। হাজার ছয়-সাত টাকা বাকি ছিল। এখানে সেই বাকি টাকাটার কথাই বলা হয়েছে।
→ নিরুপমার বাবা রামসুন্দর এই বাকি টাকাটা বাড়ি বিক্রয় করে নিরুপমার শ্বশুর রায়বাহাদুরকে) দিতে চেয়েছিলেন।
→ বক্তা নিরুপমা এই টাকা তার বাবাকে দিতে নিষেধ করেছে। নিরুপমার বাবা রামসুন্দর এবং শ্বশুর রায়বাহাদুরের মধ্যে বিত্তের দিক থেকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। কিন্তু যেখানে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, সেখানে আর্থিক অবস্থার তারতম্য হলেও পারস্পরিক মধুর সম্পর্কের আশা করতে পারা যায়। কিন্তু আশা মত কাজ হয়নি।
বিবাহের রাত্রি থেকেই মনান্তর। সেই মনান্তর ও অশান্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল। বধুর প্রতি শ্বশুরবাড়ির নিষ্ঠুর অবহেলা এবং হৃদয়হীন নির্যাতন যেন বুঝিয়ে দিল, বাবা পুরো দাম না দিতে পারার জন্যই মেয়ে পুরো যত্ন পাচ্ছে না। শ্বশুর-শাশুড়ির এই মনোভাব নিরুপমার কাছে অসহ্য।
তার জাগ্রত আত্মমর্যাদাবোধ তাকে শিখিয়েছে, নারীরা কেবল টাকার থলি নয়; বিবাহে যে কন্যার পিতা যত টাকা দিতে পারবে, পাত্রপক্ষের কাছে সেই পাত্রীর মর্যাদা তত বৃদ্ধি পাবে এবং টাকা দিতে না পারলেই তাকে অপমান ও নিপীড়নের শিকার হতে হবে,—এ আচরণ অমানবিক।
তাছাড়া মান-মর্যাদা, স্নেহ-ভালোবাসা হৃদয়ের জিনিস; বাজারের পণ্যদ্রব্যের মতো তা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। নিরুপমার নারীত্বের পক্ষে ঐ পণের টাকা দেওয়া অপমানজনক বলে মনে করাই স্বাভাবিক।
→ বাবার প্রতি এই নিষেধ বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিরুপমার প্রতিবাদী চরিত্রটি বেশ স্পষ্ট ও উদ্দীপ্ত। রবীন্দ্রনাথ এই গল্প আদ্যন্ত প্রতিবাদমুখর। আমাদের দেশে যুগে যুগে পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে মেয়েরা আত্মবলি দিয়েছে। কত সোনার প্রতিমা চিতায় উঠেছে। গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বলেছে। শাড়িতে ফাঁস লাগিয়ে উদ্বন্ধনে ঝুলেছে। কিন্তু প্রতিবাদ তেমন ভাবে কখনো উচ্চারিত হয়নি।
→ নিরুপমা ঐ সব নির্যাতিত মেয়েদেরই একজন। গল্পের প্রথম দিকে সে তেমন সক্রিয় নয়। বিবাহরাত্রির ভাগ্যবিপর্যয়ের অশুভ সূচনার সময় সে নীরব; অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠেছিল, ব্যস, ঐ পর্যন্ত। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় সে বলেছিল,—“তারা কী আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।” বাবার সান্ত্বনা সত্ত্বেও নিরুপমার আশঙ্কা শেষপর্যন্ত সত্য হয়ে গিয়েছিল।
সমস্ত অপমান, গঞ্জনা বিনা প্রতিবাদে সে সহ্য করেছিল নিজের বাবা ও ভাইদের মুখ চেয়ে। তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাবার পুনঃ পুনঃ অপমান ও লাঞ্ছনা সে আর সহ্য করতে পারল না। তাই শ্বশুরকে টাকা দেবার বিরুদ্ধে শেষে সে প্রতিবাদ জানাল। এই তীব্র প্রতিবাদই রবীন্দ্রনাথ শুনতে চেয়েছিলেন, শোনাতে চেয়েছিলেন।
নিরুপমা তাই রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহীসত্তার বাক-প্রতিমা আবার আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে বাবা ভাই প্রভৃতি আত্মীয়দের প্রতি আনুগত্য ও স্নেহ মমতায় । সে কোমল ও করুণ।
প্রশ্ন । “নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল।”—নিরুপমা কে? শরশয্যা’ শব্দটির তাৎপর্য কি? কি কারণে নিরুপমার পক্ষে শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হয়ে উঠেছিল? এর ফলে তার জীবনে কি পরিণাম ঘটেছিল তা লেখ।
বা, নিরুপমা কে? ‘শরশয্যা’ কথাটি এখানে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? নিরুপমার পক্ষে তার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হয়ে উঠেছিল কেন? এর ফলে তার জীবনের কী পরিণতি হয়েছিল
উত্তর : নিরুপমা রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ ছোটগল্পের নায়িকা; সে রামসুন্দর মিত্রের কন্যা এবং রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ। লেখো।
→ ‘শরশয্যা’ হচ্ছে শর অর্থাৎ তীরের বিছানা। ‘শরশয্যা’ শব্দটি মহাভারত থেকে গৃহীত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে সর্বাঙ্গ বিদ্ধ হয়ে কুরু সেনাপতি পিতামহ ভীষ্মের পতন হয়। কিন্তু তিনি ঐ শরজালে বিদ্ধ হয়েও জীবিত থাকেন। তাঁর সমস্ত দেহটি মাটি থেকে ওপরে শরের ওপর শায়িত ছিল।
এই শয্যা মোটেই সুখের ছিল না, ছিল তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় জর্জরিত নিরুপমার যন্ত্রণাদায়ক জীবনকে বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ ভীষ্মের এই শরশয্যার উপমাটি গ্রহণ করেছেন। —বাংলাতে এই উপমা একটি প্রবাদ বাক্য বিশেষ।
→ নিরুপমার বিবাহ বাসরে নিরুপমার বাবা বরপণের সব টাকা দিতে পারেননি, এবং পাত্র শেষ পর্যন্ত পিতার অমতে বিবাহ করেছিল। এর ফলে প্রথম থেকেই শ্বশুরবাড়িতে নিরুপমার আদরযত্ন মান-মর্যাদা কিছুই ছিল না। নিরুপমার বাবা রামসুন্দর একবার অনেক কষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে নিরুপমার শ্বশুর রায়বাহাদুরকে দিতে গিয়েছিলেন।
কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবেন না বলে তিনি সেই সামান্য টাকা স্পর্শ করেননি। এদিকে বিবাহের পর নিরুপমা একবারও বাপের বাড়ি আসতে পায়নি। তাই রামসুন্দর ছেলেদের লুকিয়ে বসতবাড়ি বিক্রি করে টাকা নিয়ে গেলেন নিরুপমার শ্বশুরকে দেবার জন্য। বারবার আঘাত পেয়ে নিরুপমার মর্যাদাবোধ এবার ‘জাগ্রত’ হল এবং বাবাকে সে দৃঢ়ভাবে জানাল, আর একটা টাকাও যদি রায়বাহাদুরকে দেওয়া হয়, তাহলে মেয়ের মুখ তিনি আর দেখতে পাবেন না।
রামসুন্দর অগত্যা ফিরে এলেন, কিন্তু ঘটনাটি পরে জানতে পেরে নিরুপমার শ্বশুর-শাশুড়ি আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ, ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন। এইভাবে নিরুপমার পক্ষে তার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হয়ে উঠল।
শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। বেশ কিছু দিন শরশয্যায় থাকার পর তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। নিরুপমার জীবনেও ঘনিয়ে এল এক শোচনীয় পরিণাম, বেচারিকে বেছে নিতে হল স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ। এবং কিছু দিন পরে বাপ বিবাহের পুরা দাম না দেওয়ার অপরাধে মেয়ের পুরো যত্ন তো বন্ধই হয়েছিল, এখন নিরুপমার খাবার দিতেও দাসদাসীরা প্রায়ই ভুল করতে লাগল।
নিজেকে দাসদাসীদের কৃপার পাত্রী ভেবে নিরুপমাও আর তাদের খাবারের কথা স্মরণ করিয়ে দিত না। অনাদরের খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে শাশুড়ি বিদ্রুপ করে বলতেন, নবাবের বাড়ির মেয়ের গরিবের বাড়ির অন্ন রুচবে কেন!
→ এই হৃদয়হীন অবহেলা এবং গঞ্জনা নিরুপমাকে ধীরে ধীরে তার নিজের জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ করে তুলল। সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। যেদিন সন্ধ্যায় নিরুপমার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হল, সেদিনই প্রথম তাকে ডাক্তার দেখতে এল এবং সেদিনই তার শেষ। মৃত্যুর পর চন্দনকাঠের চিতায় খুব ঘটা করে নিরুপমাকে দাহ করা হল; শ্রাদ্ধও হল মহা সমারোহে।
→ জীবিত অবস্থায় যারা তাকে একবিন্দু স্নেহমমতা দিল না, বেঁচে থাকবার অন্নজলটুকুও যারা বন্ধ করে দিয়েছিল, সেই তারাই তাকে মৃত্যুর পর চন্দনকাঠে দাহ করে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের
চেয়েও বধূ বিসর্জনের আয়োজন করল মহা পণপ্রথার পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, নিরুপমার জীবন পরিণামের মধ্যে দিয়ে তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন।
প্রশ্ন । “এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।”—আগের বারে কত
হাজার টাকা পণের কথা হয়? এবারে বিশ হাজার টাকা পণ হাতে হাতে আদায়ের কথা ওঠে ? আগের বারে পণের টাকা শোধ করতে না পারায় কী মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে আগের বার অর্থাৎ রায়বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের প্রথম বারের বিবাহে বরপণ নির্ধারিত হয়েছিল নগদ দশ হাজার টাকা এবং তৎসহ বহু দানসামগ্রী।
→ প্রথমবারের বিবাহে পাত্রী ছিল রামসুন্দর মিত্রের স্নেহের কন্যা নিরুপমা। রামসুন্দর সচ্ছল অবস্থার মানুষ ছিলেন না। তবু কন্যার সুখের জন্য তিনি ধনী রায়বাহাদুরের ডেপুটি পুত্রকে হাতছাড়া করতে চাননি। তাই নিজের অবস্থার কথা বিবেচনা না করেই দানসামগ্রী এবং দশ হাজার টাকা পণ দিতে রাজি হয়েছিলেন।
কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বিবাহের সময় পণের সব টাকা তিনি দিতে পারলেন না। রায়বাহাদুর সম্পূর্ণ টাকা না পাওয়ায় বর সভাস্থ করতে আপত্তি করলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র পিতার অবাধ্য হয়ে বিবাহ করল। এতে অশান্তি অনেক হল, কিন্তু পণের বাকি টাকাটা রায়বাহাদুর কোনভাবেই বেহাইয়ের কাছ থেকে আদায় করতে পারলেন না। পরে তাঁরা আর ওইভাবে ঠকতে চান না। তাই বাজার দর বৃদ্ধির মতনই বিয়ের পণ দশ হাজার’ থেকে উঠল বিশ হাজারে এবং আর ধার-বাকি নয়, হাতে হাতে নগদ আদায়ে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
আগের বারের পণের টাকা শোধ দিতে না পারার ফলে বধূ নিরুপমার শ্বশুরবাড়িতে আদর যত্ন বা সম্মান কিছুই ছিল না। তার বাবাকেও কুটুম্বগৃহে প্রতিনিয়ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হত। মেয়ের সঙ্গে বহু কষ্টে কিছুক্ষণের জন্য দেখা মিলত। তার বাপের বাড়ি আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অগত্যা রামসুন্দর পণের টাকা কিছু সংগ্রহ করে রায়বাহাদুরকে দিতে গেলেন, কিন্তু সামান্য টাকা নিয়ে তিনি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাইলেন না।
অগত্যা রামসুন্দর গোপনে বসতবাড়ি বিক্রি করে পুরা টাকা যোগাড় করে রায়বাহাদুরকে দিতে গেলেন। কিন্তু রামসুন্দরের বড় ছেলে হরমোহন জানতে পেরে সেখানে গিয়ে কাতরভাবে বাবাকে বাধা দিল। তখন অভিমানী নিরুপমা জানাল, তার শ্বশুরকে আর একটা পয়সাও যদি দেওয়া হয়, তবে সে আত্মহত্যা করবে। তাই রামসুন্দর রায়বাহাদুরকে টাকা না দিয়ে ফিরে চলে এলেন।
কিন্তু টাকা নিয়ে এসে না-দেবার ব্যাপারটা জানাজানি হলে, নিরুপমার শ্বশুর শাশুড়ি তার ওপর বেশি করে নির্যাতন শুরু করল এবং নিরুপমাও উপায়ান্তর না দেখে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিল। আহার নিদ্রার অনিয়মে সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হল এবং বিনা চিকিৎসায় শেষে তার মৃত্যু হল। এইভাবে পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে নিরুপমাকে মর্মান্তিকভাবে বলি দেওয়া হল।
দেনাপাওনা গল্পের ছোট প্রশ্ন উত্তর
প্রশ্ন : । “টাকা যদি দাও তবেই অপমান।”—উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
বা,’—কার উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দেনাপাওনা’ শীর্ষক ছোটগল্পের বরপণের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্তা নিরুপমার এই উক্তি তার বাবা রামসুন্দরকে উদ্দেশ করে।
→ এই মর্যাদাব্যঞ্জক উক্তি বিশেষ তাৎপর্যবহ। পরিবারের সবাইকে পথে ভাসিয়ে বসতবাড়ি বিক্রি করে কন্যাগত-প্রাণ রামসুন্দরের অর্থ সংগ্রহের গোপন তথ্য জেনে নিরুপমার মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠল তার অন্তরতর নারীসত্তা ও নারীত্বের মর্যাদাবোধ। সে উপলব্ধি করল যে, সে পণ্য সামগ্রী নয়, সে নারী।
পণের টাকার অঙ্কে পাত্রীর জীবনের মূল্য স্থির হতে পারে না। পিতা রামসুন্দর প্রতিশ্রুত বরপণের অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করে নিজেকে এবং স্নেহের কন্যাকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নিরুপমার বিদ্রোহী নারীসত্তা এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত থেকে পিতাকে নিবৃত্ত হতে বলল। সে দৃঢ়ভাবে জানাল, অর্থলোলুপ শ্বশুরকে অর্থ দিলেই বরং তার নারীত্বের সম্মান বিসর্জিত হবে।
সে কী কেবল একটি টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে, ততক্ষণই কী তার দাম? অর্থলিপ্স শ্বশুর রায়বাহাদুরকে বরপণের অবশিষ্ট টাকা দেওয়ার অর্থই হ’ল, লোভীকে প্রশয় দেওয়া এবং সেই সঙ্গে তার নারীত্বের অপমান।
প্রশ্ন : । “আমি কী কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।” —বক্তা ও শ্রোতা কে? শ্রোতাকে বক্তা যে বলেছে, সে টাকার থলি নয়, তার এ মনোভাব কী সমর্থন কর?
• উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে শ্বশুরবাড়ির নির্যাতিতা বধূ নিরুপমা এখানে বক্তা এবং শ্রোতা হলেন নিরুপমার বাবা রামসুন্দর মিত্র।
→ রামসুন্দরের প্রতি নিরুপমার বক্তব্যের মধ্যে তার যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, তা যে-কোন মর্যাদাসম্পন্ন মানবতাবাদী মানুষ সমর্থন করবেন। তাই পাঠক হিসেবে আমরাও এ মনোভাব সমর্থন করি। পণের টাকা না দিতে পারার অপরাধে নিরুপমা এবং তার বাবাকে রায়বাহাদুরের বাড়িতে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে।
কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। নিরুপমা সর্বনাশের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে সমাজের এই নিকৃষ্ট পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। টাকার জন্য যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব, নারীর নারীত্ব, আত্মীয়তার মাধুর্য্য পদদলিত হয়,
সেই অর্থলিপ্স প্রথাকে ক্ষমা করা যায় না। টাকার বিনিময়ে মেয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কেনা নারীত্বের অপমান, মনুষ্যত্বেরও অপমান। এইজন্যই নিরুপমা বিদ্রোহী হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে রায়বাহাদুরকে লোভের টাকা যোগান দেবার বিরুদ্ধে। কারণ নারীর মর্যাদা ও নারীত্বকে টাকা দিয়ে বেচাকেনা করা যায় না।
নিরুপমার মত যারা পণপ্রথার বলি, তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, যারা নির্যাতিত, তারা নিজেরা না-এগিয়ে এলে তাদের সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারবে না।
প্রশ্ন : ১৮। “বাড়ির বড়ো বউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।”—‘বড় বউ’ কে? ‘খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া’ কেন হল তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
উত্তর : বাড়ির ‘বড়ো বউ’ বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দেনাপাওনা’ শীর্ষক ছোটগল্পের রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ নিরুপমাকে বোঝাচ্ছে।
→ মৃত্যুর পর নিরুপমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয়েছিল খুব ঘটা করে। সৎকার করা হয় মহাসমারোহে। অমন চন্দনকাঠের চিতা ঐ অঞ্চলে কেউ কখনো আগে দেখেনি। শুধু শবের সৎকার নয়, শ্রাদ্ধের সমারোহও কম ঘটা করা হয়নি।
রায়বাহাদুররা এসব ব্যাপারে রায়চৌধুরীদের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের নামডাককেও টেক্কা দিতে চেয়েছিলেন। তাই কিঞ্চিৎ ঋণ করে সাধ্যাতিরিক্ত খরচপত্রে তাঁরা ঐ শ্রাদ্ধ করেছিলেন। জীবিতকালে নিরুপমাকে তাঁরা তার বধূজীবনে যে অশেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও নির্যাতন দিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর মহাসমারোহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে যেন সেই বধূ নির্যাতনের চিত্রকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।
জীবনে যাকে বেঁচে থাকতে বিন্দুমাত্র আদর যত্ন করা হয়নি, উপরন্তু বিনা চিকিৎসায় যার মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল, তার অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধকে ঘিরে এই সমারোহ যে কী নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীনতার পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ সরস ব্যঙ্গের দ্বারা তা তীব্রভাবে এই বাক্যে প্রকাশ করেছেন।
দেনাপাওনা গল্পের প্রশ্ন




