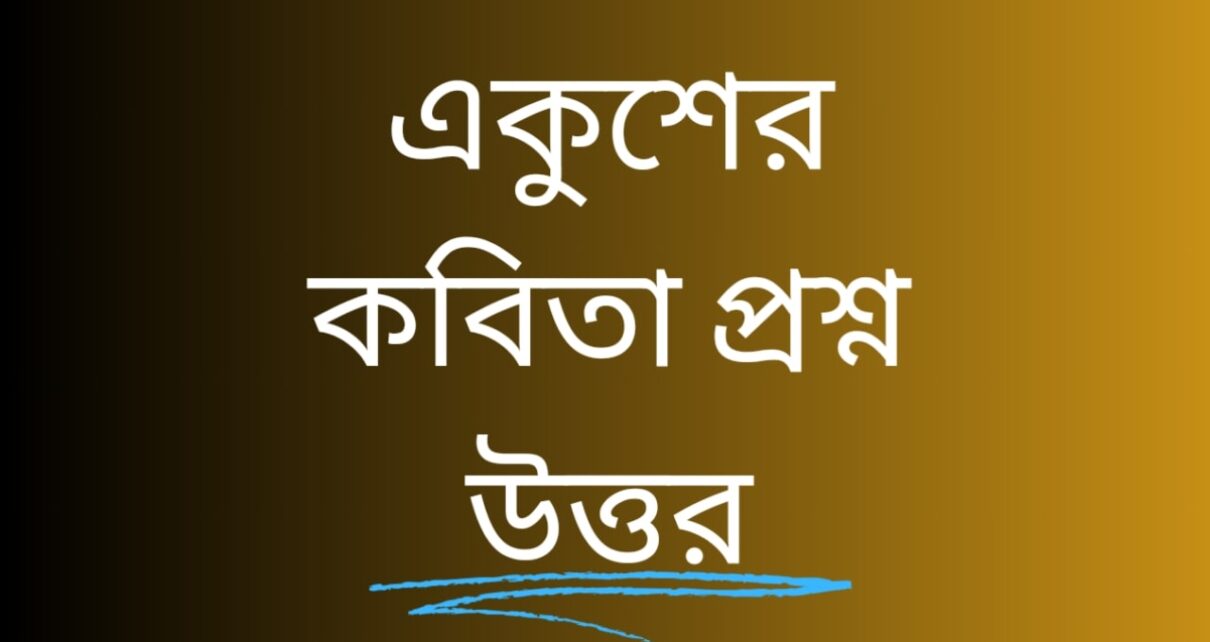একুশের কবিতা প্রশ্ন উত্তর Study Learn
একুশের কবিতা
আশরাফ সিদ্দিকী
একুশের কবিতা বিষয়বস্তু, একুশের কবিতা অনুশীলনী প্রশ্ন উত্তর, এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা হয়েছে।
একুশের কবিতা
একুশের কবিতা বিষয়বস্তু:

বিষয়সংক্ষেপ
মাতৃভাষার প্রতি অসাধারণ টান ‘একুশের কবিতা’র মধ্যে অনিবার্যভাবে গাঁথা হয়ে আছে। কবির চেতনায় একুশে ফেব্রুয়ারির
শহিদদের কথা উজ্জ্বল। শৈশবে পড়া ‘পাখি সব করে রব’ কবিতাটি যেন মন্ত্রের যেন মন্ত্রের মতো বাজছে স্মৃতির গভীরে। মাতৃভূমি বাংলাদেশ,
মাটির গান ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, জারি, সারি গান শৈশবে মায়ের গাওয়া নানা গানের কলি, বিন্নিধান—এসবের পাশাপাশি কবির মনে আসছে তাদের কথাও উনিশশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে খাজা নাজিমুদ্দিন সরকারের পুলিশ গুলি করে মেরেছিল যাদের। ইতিহাস লিখে নিয়েছে সেই বেদনাময় ঘটনা, বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে রক্ষার সেই করুণ কাহিনি।
একুশের কবিতা সারমর্ম :
কবির বয়ানে ঝরে পড়া কয়েকটি পাখি আসলে ভাষা-শহিদ আর সহস্র পাখি হল আপামর মানুষ, যারা ভাষার জন্য পা মেলায় মিছিলে, যার মধ্যে কবি দেখেন মা-কে। সহস্র সহস্র বাঙালি তাঁদের মাতৃভাষায় কথা বলে। কবির মা, যিনি বাংলা ভাষায় কথা বলেন তিনি কথায় কথায় রূপকথা, কথকতা, বাংলা ছড়ার ছন্দে সুরের ফুল ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর মিছিলে গাইছেন—‘পাখি সব করে রব’।
নামকরণ
সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর কবিতার নামকরণ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে তার বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করতেই হবে। আলোচ্য কবিতাটি যে পটভূমিতে রচিত হয়েছিল সেই পটভূমির সঙ্গে ইতিহাসের একটা গভীর যোগ রয়েছে।
যা ভারত ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছিল। জন্ম হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান দুটি স্বাধীন দেশের। পাকিস্তানের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান আজ স্বাধীন বাংলাদেশ নামে পরিচিত। এই দুই পাকিস্তান ভাগ হয়েছিল ভাষাগত কারণে।
পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ পূর্ব পাকিস্তানে জোর করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালানোর চেষ্টা করলে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষ এর তীব্র বিরোধিতা করে। এর ফলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের খাজা নিজামুদ্দিন সরকারের পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়।
এর ফলে মারা যান আব্দুস সালাম, আবুল বরকত, সফিউর রহমান, রফিক-উদ্দিন আহমেদ ও আব্দুল জব্বার। এই পাঁচ ভাষা শহিদের মৃত্যুতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষজন তীব্র আন্দোলনে নেমে পড়ে যা থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।
এই ইতিহাসেরই ছায়াপাত ঘটেছে ‘একুশের কবিতা’য়। তাই ভাষার প্রতি আবেগে দেশপ্রেমিক কবি তাঁর এই কবিতায় ভাষা মুগ্ধতার প্রচার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই কবিতার নামকরণ ‘একুশে’ শব্দটি যেন মন্ত্রের মতো উচ্চারণে যুক্ত হয়েছে। আর নামকরণটিও সার্থকতা লাভ করেছে।
একুশের কবিতা অনুশীলনী প্রশ্ন উত্তর :
প্রশ্নোত্তর বিভাগ
হাতেকলমে
১.এই কবিতায় কিছু চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ‘কাঁপলো’ এবং দাঁড়িয়েছেন’। প্রসঙ্গত দুটি শব্দই ক্রিয়া। চন্দ্ৰবিন্দু দিয়ে শুরু এমন পাঁচটি অন্য ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য লেখো :
শব্দ
১.১ কাঁদালো = বাচ্চাটি বেশ খেলছিল, অনেকক্ষণ মাকে না দেখতে পেয়ে কাঁদলো।
১.২ হাঁটলো = ১৫ আগস্টের পদযাত্রায় শিক্ষকমহাশয়দের সঙ্গে ছাত্ররাও হাঁটলো।
১.৩ গাঁথলো = ঠাকুরের গলায় দেবার জন্য রমা ফুল তুলে মালা গাঁথলো।
১.৪ চ্যাঁচালো = দলকে জেতাবার জন্য সমর্থকরা খুবই চ্যাঁচালো।
১.৫ বাঁধলো = অনেকদিন পর মা নিজের হাতে প্রিয় একটি পদ বাঁধলো।
২. গুনগুন : মৌমাছি যেভাবে ডানার একটানা আওয়াজ করে, তাকে গুনগুন বলে। বাস্তব ধ্বনির অনুকরণে তৈরি হওয়া এই ধরনের শব্দকে বলে অনুকারী বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ। নীচে কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ শিখে নিতে পারবে :
পাখা = বন বন করে ঘুরছে।
মাছিটা = ভন ভন করে উড়ছিল।
হওয়া = সন সন করে বইছে।
নদী = চলেছে কল কল রবে।
কাচের = বাসনগুলি ঝন ঝন করে ভেঙে গেল।
বাজ = পড়ল কড় কড় শব্দ করে।
পটকা = ফাটছিল দুমদাম করে।
বৃষ্টি = পড়ছিল ঝর ঝর করে।
কাগজটা = ফর ফর করে ছিড়ে গেল।
কয়েকটা তাল = পড়ল ধুপধাপ করে।
৩. আমার মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি’—এখানে ‘মায়ের গাওয়া’ শব্দবন্ধটি একটি বিশেষণের কাজ করছে। এরকম আরো অন্তত পাঁচটি তৈরি করো :
উত্তর: বিশেষণ
১.মায়ের বলা রূপকথা।
২. দিদির রাঁধা পায়েস।
৩. দাদার দেওয়া ঝর্ণা কলম।
৪. ভাইয়ের লেখা গান।
৫. মাসির বানানো পুতুল।
৪. নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তন করে বাক্যরচনা করো :
সুর, দেশ, মাঠ, বন, মিষ্টি, মুখর, ইতিহাস, ফুল।
বিশেষ্য – বিশেষণ
সুর – সুরেলা = তোমার সুরেলা গলায় গান আমার ভালো লাগে।
দেশ – দেশি = মায়ের দেওয়া দেশি কাপড়ই আমার পছন্দ।
মাঠ – মেঠো = মেঠো সুরে গান গাইছে মধুদাদা।
বন- বুনো = তোমায় নাকি বুনো বেড়াল তাড়া করেছিল?
মিষ্টতা- মিষ্টি = সম্পর্ক ভালো থাকে কথার মিষ্টতায়।
মুখরতা – মুখর = আজ তোমাদের পাড়া মুখরতার পরিপূর্ণ থাকবে।
ইতিহাস- ঐতিহাসিক = ঐতিহাসিক রমেশ সেন আমার বাবার বন্ধু।
ফুল- ফুলেল = ফুলেল তেলের গন্ধ আমার ভালো লাগে।
৫. ‘’রব’ শব্দটিকে একবার বিশেষ্য এবং একবার ক্রিয়া
উত্তর
হিসেবে দুটি আলাদা বাক্যে ব্যবহার করে দেখাও :
শব্দ – শব্দরূপ – বাক্য
রব – বিশেষ্য = আজ পাখির রবে ঘুম ভাঙল।
রব – ক্রিয়া = হইহই রবে ছুটে এল সবাই।
৬. ‘কলি’, ‘সুর’, ‘পাল’—শব্দগুলিকে দুটি করে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে আলাদা বাক্যে লেখো :
উত্তর
শব্দ – ভিন্ন অর্থ – বাক্য
কলি – কুঁড়ি = গোলাপ গাছে কত কলি এসেছে।
কলি – গানের পঙক্তি = বিন্দিতা গুনগুন করে একটা চেনা গানের কলি ভাঁজছে।
সুর – সংগীতের স্বর = একটা পুরোনো সুর শোনালে তুমি।
সুর – দেবতা = অসুরেরা একদিন সুরের কাছে পরাজিত হয়।
পাল – দল = রাখাল গোরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে।
পাল – নৌকায় ব্যবহৃত = এবার নৌকার পাল তুলে দাও।
৭. ‘মুখ’শব্দটিকে পাঁচটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে পাঁচটি আলাদা বাক্য লেখো :
শব্দ – ভিন্ন অর্থ – বাক্য
মুখ তোলা – প্রসন্নতা অর্থে = দেবতা মুখ তুলে তাকালেন বলেই তো রুগ্ণ ছেলেটা সুস্থ হল।
মুখ উজ্জ্বল – গৌরবান্বিত = ভালো রেজাল্ট করে ছেলেটা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে।
মুখ খারাপ – কুবাক্য = কথায় কথায় মুখ খারাপ করা তার অভ্যাস।
মুখ ঝামটা – ভর্ৎসনা = মুখ ঝামটা মেরে কথা বোলো না কাউকে।
মুখ ভার – অভিমান = বাবার কাছে কিছু টাকা চেয়ে পেল না বলে বুবাই তার মুখ ভার করে রইল।
৮. একটি-দুটি বাক্যে উত্তর দাও :
৮.১ “পাখি সব করে রব”—উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ ? কবিতাটি তাঁর কোন বইতে রয়েছে?
উঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘প্রভাতবর্ণন’ কবিতার অংশ। কবিতাটি কবির ‘শিশুশিক্ষা’ (প্রথম ভাগ) গ্রন্থে আছে।
৮.২ এই পঙ্ক্তিটি পাঠের সুরকে মন্ত্রের মতো’ বলা হয়েছে কেন?
উঃ শৈশবে পাঠশালায় পড়া এই পক্তি মন্ত্রের ছন্দের মতোই পবিত্র বাক্য মনে হয়েছে কবির। মন্ত্র যেমন বার বার উচ্চারিত হয়, এই পঙ্ক্তিটিও তেমনি দুলে দুলে পাঠ করা হয়।
৮.৩ এই সুরকে কেন ‘স্মৃতির মধুভাণ্ডার’ বলা হয়েছে? তা কবির মনে কোন স্মৃতি জাগিয়ে তোলে?
উত্তর এই সুর কবির শৈশবের মধুর স্মৃতিগুলিকে জাগিয়ে দেয়, তাই একে ‘স্মৃতির মধুভাণ্ডার’ বলা হয়েছে।
এই সুর কবির মনে তাঁর দেশ-মাঠ-বন-নদী, দেশের জারিসারি-ভাটিয়ালি-মুর্শিদি গান এবং মায়ের মুখ মনে করিয়ে দেয়।
৮.৪ “সেই আমার দেশ-মাঠ-বন-নদী”—দুই বঙ্গ মিলিয়ে তিনটি অরণ্য ও পাঁচটি নদীর নাম লেখো।
অরণ্য—সুন্দরবন, জলদাপাড়া, গোরুমারা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোলা ও মধুমতি।
নদী—গঙ্গা, পদ্মা, তিস্তা, মেঘনা, বুড়িগঙ্গা।
৮.৫ টীকা লেখো : জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিন্নি ধান, কথকতা, রূপকথা।
উত্তর জারি : ফারসি শব্দ, ‘জারী’ বা ‘যারী’ থেকে এই শব্দটি এসেছে। এটি বাংলার মুসলমানি পল্লিগীতিবিশেষ, যা মুসলিম শোকগাথা হিসেবেও পরিচিত। বাংলাদেশের ইসলামধর্মী লোকশিল্পীরা কারবালার প্রান্তরে হাসান-হোসেনের শোকাবহ মৃত্যুকে স্মরণ করে উদাও কণ্ঠে এই পল্লিগান গেয়ে থাকেন।
সারি : তুরস্কের শব্দভাণ্ডার তথা তুর্কি শব্দ থেকে বাংলায় শব্দটির আগমন। এটিও বাংলাদেশের একপ্রকার লোকগীতি, মূলত মাঝিমাল্লাদের গান। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লারা নদীর খোলামেলা পরিবেশে সুরেলা কণ্ঠে দ্রুত ছন্দের এই গান গেয়ে থাকেন। এই বীররসের গান সমবেত কণ্ঠেও ধ্বনিত হতে দেখা যায়।
ভাটিয়ালি : ‘ভাটিয়ালি’ শব্দটি যে অর্থ বহন করে আনে, তা আসলে সুর। ভাটার টানে নৌকো ভাসিয়ে বিশেষ রাগণীতে এই সুর মাঝিমাল্লাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। এটি বাংলার লোকসংস্কৃতিতে এক বিশেষত্বময় এমন এক সুরের প্রবাহ, যা সকল মানুষকে মুগ্ধ
মুর্শিদি : মুসলমান সাধক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় পির। ‘মুর্শিদি’ হল সেই পিরদের গান। এই গানে থাকে বাস্তবতা। সংকেতের মাধ্যমে দেহতত্ত্বকে এই গানে প্রকাশ করা হয়, থাকে লৌকিক উপমা। সব মিলিয়ে এই গানকেও পল্লিগীতি
৮.৬ তোমার জানা দুটি পৃথক লোকসংগীতের ধারার নাম লেখো।
উত্তর আমার জানা দুটি পৃথক লোকসংগীত ধারার নাম হল—লালনগীতি, ঝুমুর গান।
৮.৭ “ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে লিখে নিলো সব… বলতে এখানে কী কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে মৃত শহিদদের কথা এবং বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য মানুষের প্রতিবাদের কথা লিখে নিল ইতিহাস।
৮.৮ তাই তো সহস্র পাখির কলতানে আজ দিগন্ত মুখর” – সহস্র পাখি’ কাদের বলা হয়েছে?
উত্তর বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে, গান গায় -সেইসব মানুষদেরকে ‘সহস্র পাখি’ বলা হয়েছে।
৯. ব্যাখ্যা করো :
৯.১] “কয়েকটি পাখি…পড়ে গেল মাটিতে ”।
উত্তর:- উৎস : উদ্ধৃতাংশটি কবি আশরাফ সিদ্দিকীর ‘একুশের কবিতা’ থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গ : মাতৃভাষা বাংলার জন্য ভাষা-শহিদদের স্মরণ করে
তাৎপর্য : ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি খান সেনাদের গুলিতে যে পাঁচজন তাজা তরুণ প্রাণ হারায়, তাদের কবি ‘পাখি’ বলেছেন। তারাই ঝরে গেছে অকালে ভাষা আন্দোলনে প্রাণ দিয়ে।
৯.২ ‘সেই শোকে কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো আকাশে’।
উত্তর:- উৎস : উদ্ধৃতাংশটি কবি আশরাফ সিদ্দিকীর ‘একুশের কবিতা’ থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গ : মাতৃভাষা বাংলার জন্য যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাদের কথা উল্লেখ করতে গিয়েই কবি এ কথা বলেছেন।
তাৎপর্য : ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে পাঁচজন তাজা-তরুণ প্রাণ ঝরে পড়ে ঢাকার রাজপথে। কেঁপে ওঠে মাঠ-ঘাট-বাট-হাট-বন-মন। সমস্ত দেশ জুড়ে ওঠে প্রতিবাদের ঝড়। গণ-আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এই গণ-আন্দোলনকেই কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
৯.৩ ‘কথায় কথায় কথকতা কতো রূপকথা’।
উত্তর:- উৎস : উদ্ধৃতাংশটি কবি আশরাফ সিদ্দিকীর ‘একুশের কবিতা’ থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গ : মা, যিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসেন তিনি কথায় কথায় কথকতা করেন এবং রূপকথা বলেন।
তাৎপর্য : আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা। আমাদের মা বাংলা ভাষাতেই আমাদের কথকতা রূপকথা আর ছড়া শোনান। মায়ের ভাষা আমাদের মাতৃভাষা।
[৯.৪] ‘তাই তো আজ দ্যাখো এ মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার মা’।
উত্তর উৎস : উদ্ধৃতাংশটি কবি আশরাফ সিদ্দিকীর ‘একুশের কবিতা’ থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গ: মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য সবার সঙ্গে মা-ও এসে দাঁড়িয়েছেন। কারণ তিনিও বাংলা ভাষায় কথা বলেন।
তাৎপর্য : মাতৃভাষা মায়ের মুখের ভাষা। মুখের ভাষা প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো দেশের জাগরণ সম্ভব নয়। তাই মিছিলে মা এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে।
১০ আট-দশটি বাক্যে উত্তর দাও :
(১০.১) এই কবিতায় ‘পাখি’ শব্দের ব্যবহার কতখানি সার্থক হয়েছে তা কবিতার বিভিন্ন পড়ক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা করো।
উত্তর:- ‘পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।’—এই পঙ্ক্তিতে ‘পাখি’ শব্দটিকে কবি রূপক হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। পাখির প্রথম কলকাকলিতে রাত শেষ হয়। দেশের কিশোর তরুণ জেগে উঠলে শেষ হয় অন্যায়ের রাত। ভাষা আন্দোলনে এরকমই তরতাজা যুবকরা প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল।
তাই কবি লিখেছেন—’কয়েকটি পাখির গান শেষ না হতেই তারা ঝরে গেলো, ‘ কিন্তু ইতিহাস তা লিখে নিয়েছিল। তাই সারা বিশ্ব পরবর্তীকালেও মাতৃভাষা ও তার সম্মান নিয়ে মুখরিত হয়েছে। তাই কবি লিখেছেন—
‘সহস্র পাখির কলতানে আজ দিগন্ত মুখর|’
১০.২ কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।
উত্তর:- বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কবি আশরাফ সিদ্দিকীর ‘একুশের কবিতা’-র মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অত্যুজ্জ্বল ইতিহাসকথা। অধুনা বাংলাদেশের মাতৃভাষাপ্রেমী ভাষা-আন্দোলনকারীদের প্রিয় ২১ ফেব্রুয়ারির ইতিকথা। আশ্চর্য সংযমে কবি সারা কবিতার কোথাও একটিবারের জন্য ‘একুশে’ শব্দটি উচ্চারণ করেননি, অথচ সমগ্র কবিতাটির অঙ্গে তিনি শৈল্পিক দক্ষতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন একুশের ভাষা-আন্দোলনের প্রলেপ।
‘একুশের কবিতা’র মধ্যে ধরা আছে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ইতিহাস, যার মূলে রয়েছে মাতৃভাষার মর্যাদা ও ঐতিহ্যরক্ষার আত্মিক প্রচেষ্টা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে দ্বিখণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষার উপর উর্দুকে বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায় পূর্ববঙ্গে। মিছিলের উপর সেনাদের গুলিবর্ষণে পাঁচ মাতৃভাষাপ্রেমিক তরুণের মৃত্যু হলে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গের মানুষ।
মাতৃভাষাকেন্দ্রিক এই গণ-আন্দোলনের সূচনা হয় ২১ ফেব্রুয়ারিতেই। এই আন্দোলনে বিজয়ী হন আন্দোলনকারীরা, জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের, জয় হয় বাংলা ভাষার। এই আন্দোলন, এই মরণপণ লড়াই, এই বিজয়ের স্মরণেই ‘একুশের কবিতা’। স্বভাবতই কবিতায় একুশে শব্দটির অস্তিত্ব ধরা না পড়লেও নামকরণে কবি একুশে শব্দটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রয়োগ করতে ভোলেননি। নামকরণটি তাই সার্থক।
১১.“শুধু মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়বদ্ধতার প্রকাশ নয়, এই কবিতায় রয়েছে আবহমানের ও অমরতার প্রতি বিশ্বাস”—পাঠ্য কবিতাটি অবলম্বনে উপরের উদ্ধৃতিটি আলোচনা করো।
উত্তর:- মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো। এর মাধ্যমেই মানুষের আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশ। তাই কোনো মানুষই মাতৃভাষার অপমান সহ্য করতে পারে না। কবিও মাতৃভাষামুখিন, তাঁরও আত্মপ্রকাশ বা আত্মবিকাশ মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই।
‘একুশের কবিতা’য় তিনি মাতৃভাষার প্রতি কেবল অসীম শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেননি, এই ভাষার প্রতি তাঁর গভীর দায়বদ্ধতা ও এর আবহমানতা বা অমরতার প্রতি তাঁর বিশ্বাসও কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। কবি মনে করেন ভাষার একটা নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। এই কবিতায় সেই ঐতিহ্যেরই স্মারক করে তিনি এনেছেন মাতৃভাষার সুধামাখানো কথকতা-রূপকথার আশ্চর্য উন্মাদনাকে।
ভাষার স্পর্শ গায়ে মেখে জীবন্ত হয়ে ওঠা জারি-সারি-ভাটিয়ালি-মুর্শিদি ইত্যাদি লোকগীতির দীর্ঘ প্রবহমানতাকে তিনি প্রাণের মূল্যে যাচিত করেন। বাংলার সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট খইয়ের বিন্নিধান তাঁর কাছে মূল্য পায় স্বর্গীয়ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে। শিশুকালে পাঠশালায় দুলে দুলে পড়া বাল্য-কবিতাকে তিনি অন্যান্য বঙ্গভাষী মানুষের মতো ভুলতে পারেন না। মিছিলে এসে দাঁড়ানো মায়ের অমোঘ উপস্থিতি ও কবির মনে অমরতার ঐতিহ্যগত প্রকাশ ঘটায়।
১২. মনে করো তুমি এমন কোনো জায়গায় দীর্ঘদিনের জন্য যেতে বাধ্য হয়েছো, যেখানে কেউ তোমার মাতৃভাষা বোঝেন না। নিজের ভাষায় কথা বলতে না পারার যন্ত্রণা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।
উত্তর
ত্রিপুরা
০২.০৯.২০২৩
প্রিয় নয়ন,
আশা করি, ভালো আছিস। বাবা বদলির চাকুরির সূত্রে এখন মিজোরামে; ফলে আমরাও এখানে। এখানে কেউ বাংলা জানে না; কেবল ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। বাংলায় কথা বলতে না পারা যে কত কষ্টের, তা প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি। স্কুলে, পাড়ায় কেউ বাংলা জানে না।
কেবল বাড়িতে মা, বোন আর বাবার সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারি। এ এক ভয়ংকর যন্ত্রণা। বাবা চেষ্টা করছেন বদলির জন্যে। তুই চিঠি দিস। একটু বাংলা পড়তে পারব। কাকু-কাকিমাকে আমার প্রণাম জানাবি। ভালো থাকিস।
ডাকটিকিট
প্রেরক, ইতি তোর
বন্ধু সূর্য
সুমিত দাস প্রাপক
ত্রিপুরা নয়ন
১৩. তোমার বিদ্যালয়ে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ কীভাবে পালিত হয়ে থাকে, তা জানিয়ে প্রিয় বন্ধুকে চিঠি লেখো।
উত্তর
প্রিয় অনামিকা,
সিমলা
২১.০২.২০২৪
আশা করি, তুই ভালো আছিস, আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজ ২১ ফেব্রুয়ারি, এই দিনটা আমাদের বিদ্যালয়ে কীভাবে পালিত হল, তা জানিয়েই এই চিঠিটা আজ তোকে লিখছি।
২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে পূর্ববাংলার মানুষ বাংলা ভাষাকে সম্মানের আসনে বসিয়েছিল। তাঁদের স্মরণে প্রতি বছরের মতো আজও আমাদের বিদ্যালয়ের শহিদ-বেদীতে মালা দেওয়া হয়, সেইসঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সংগীত, নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশন করে।
প্রধান শিক্ষিকা-সহ অন্যান্য শিক্ষিকারা ভাষা আন্দোলন ও ভাষার মর্যাদার বিষয়ে কিছু কথা আমাদের বলেন। এই বছর এই বিষয়টির উপর ‘বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতাও হয়েছে।
আশা করি তোদের বিদ্যালয়েও এই দিনকে এভাবেই স্মরণ করা হয়েছে। আজ এখানেই শেষ করছি। তুই ভালো থাকিস।
ডাকটিকিট প্রাপক,
অনামিকা সেন
উত্তরপাড়া
তোর বন্ধু
বৃষ্টি দত্ত |
একুশের কবিতা প্রশ্ন উত্তর Class 7:
অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর :
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর
সঠিক উত্তর নির্বাচন করো
উত্তর
১ পাখি সব (মন দেয় নিজ পাঠে/করে রব)।
উঃ করে রব)।
২ মায়ের মুখ মিশে আছে (কত সুরের সাথে/কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে)।
উঃ কত সুরের সাথে
৩ বিন্নিধানের মাঠে শোনা যায় (পাখির কলতান/গুলির আওয়াজ)।
উঃ গুলির আওয়াজ
৪ শোকে আকাশে উঠলো (কালবৈশাখীর ঝড়/পাখির কলতান)।
উঃ কালবৈশাখীর ঝড়
৫ দিগন্ত মুখর হয় (গুলির আওয়াজে/পাখির কলতানে)।
উঃ পাখির কলতানে
৬ শিশুগণ মন দেয় (কত সুরের সাথে/নিজ নিজ পাঠে)।
উঃ নিজ নিজ পাঠে
আমার মায়ের
© কত সুরের সাথে।
শূন্যস্থান পূরণ করো
১ পাঠশালায় পড়া —- মতো সেই সুর।
উঃ মন্ত্রের
২ আমার মায়ের — – কত না গানের কলি!
উঃ গাওয়া।
৩. —— মাঠের ধারে হঠাৎ কয়েকটি গুলির আওয়াজ।
উঃ বিন্নিধানের।
৪. শোকে —— ঝড় উঠলো আকাশে।
উঃ কালবৈশাখীর।
৫. —— থমকে দাঁড়িয়ে লিখে নিল সব।
উঃ। ইতিহাস।
অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
১.ভাটার টানে নৌকো ছেড়ে মাঝিরা কোন্ গান গায় ?
উঃ ভাটার টানে নৌকো ছেড়ে মাঝি ভাটিয়ালি গান গায়।
২.কোন্ মাঠের ধারে গুলির আওয়াজ শোনা গেল?
উঃ বিন্নিধানের মাঠের ধারে গুলির আওয়াজ শোনা গেল।
৩. কোন্ ভাষায় ‘আমার মা’ কথা বলেন?
উঃ বাংলা ভাষায় ‘আমার মা’ কথা বলেন।
৪. গোরুর পাল মাঠে কে নিয়ে যায় ?
উত্তর: রাখাল গোরুর পাল মাঠে নিয়ে যায়
৫. কারা নিজ নিজ পাঠে মন দেয়?
উঃ শিশুগণ নিজ নিজ পাঠে মন দেয়।
একমুখী তথ্যানুসন্ধানী প্রশ্নোত্তর
দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর লেখো
1. সুরের সঙ্গে কী কী মিশে আছে?
উত্তর:- সুরের সঙ্গে মিশে আছে কবির মায়ের মুখ, মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি।
2. ‘কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো আকাশে’—তাতে কী কী কাঁপলো?
উত্তরা:- আকাশে কালবৈশাখীর ঝড় উঠলে মাঠ, ঘাট, বাট, হাট, বন, মন কাঁপলো।
3.মিছিলে এসে দাঁড়ানো কবির মা-এর সম্পর্কে ‘একুশের কবিতা’ শীর্ষক কবিতায় যা বলা হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তরা মা বাংলা ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসেন। তিনি কথায় কথায় কথকতা, রূপকথা, আর ছড়ার ছন্দে মিষ্টি সুরের ফুল ছড়ান।
ৰোধমূলক প্রশ্নোত্তর
কমবেশি ছ-টি বাক্যে উত্তর লেখো
1.. ‘একুশের কবিতা’র প্রথম ও শেষাংশে কবি কেন ‘প্রভাতবর্ণন’ কবিতার পঙ্ক্তিগুলি ব্যবহার করেছেন?
উত্তর:- বিশিষ্ট কবি আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর ‘একুশের কবিতা’-র প্রথম ও শেষাংশে বিদ্যাসাগর-সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের তিন-ভাগে বিভক্ত শিশুপাঠ্য ‘শিশুশিক্ষা’ বইয়ের ‘প্রভাতবর্ণন’ কবিতায় অংশবিশেষ ব্যবহার করেছেন। কবি বঙ্গভাষী, তিনি জানেন প্রায় সব শিশুকেই ‘প্রভাতবর্ণন’-এর মতো এমন মনোমুগ্ধকর শিশু-কবিতা পড়তে হয়।
ভাষাশিক্ষায় প্রবেশের এ এক চিরায়ত পথ। ‘প্রভাতবর্ণন’ কবিতা পড়ার মধুময় স্মৃতি কবির মনকে তাঁর আলোচ্য কবিতা রচনার কাল পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই ভাষার আত্মীয়তা ও ভাষার ঐতিহ্য বোঝাতেই তিনি এই কবিতার বিশেষ অংশ নিজের কবিতায় ব্যবহার করেছেন।
2. ‘একুশের কবিতা’য় ‘আমার মা’ প্রসঙ্গটি কবি কীভাবে এনেছেন?
উত্তরা ‘একুশের কবিতা’ কবি আশরাফ সিদ্দিকীর এমন একটি কবিতা, যেখানে তিনি তাঁর বঙ্গপ্রীতি ও মাতৃভাষাপ্রীতিকে একসূত্রে গ্রথিত করে দেখেছেন। স্বভাবতই কবিতায় বঙ্গজননীই ‘আমার মা’ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাই তিনি মাতৃকণ্ঠে মাতৃভাষায় উচ্চারিত পল্লিসংগীত ও আরও কত সুরের সঙ্গে মায়ের মুখকে মিশে থাকতে দেখেন।
বাংলা শব্দে কোমল উচ্চারণের মধ্যে ‘আমার মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি’ অনুভব করেন। ভাষা-আন্দোলন যখন বিজয়ে সার্থকতা পায়, তখন তিনি দেখেন বিজয়-মিছিলে পা মেলানো আমার মা-কে, যিনি মাতৃভাষায় কথা বলতে বড়ো ভালোবাসেন, যিনি এখনো মিছিলে দাঁড়িয়েও গুণ গুণ করে গাইতে পারেন।
একুশের কবিতা বড় প্রশ্ন উত্তর :
রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর
কমবেশি আট-দশটি বাক্যে উত্তর লেখো
একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিকথা সংক্ষেপে তোমার ভাষায় বর্ণনা করো।
উত্তরা ২১ ফেব্রুয়ারির ইতিকথা আসলে এক জোরালো ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের ভিত্তিতে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তানের ভাগে পড়ে পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে কেবল স্থানিক দূরত্বেই অবস্থিত ছিল না, দুটি স্থানের ভাষা-সংস্কৃতির মধ্যেও ছিল যথেষ্ট ফারাক।
তাই যখন পশ্চিম পাকিস্তান রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর বাংলার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপানোর চেষ্টা চালায়, তখন মাতৃভাষা প্রীতি ও ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতায় উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গ।
১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের স্বার্থে এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে পাকিস্তান সরকারের পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। মারা যান আব্দুস সালাম, রফিক-উদ্দিন আহমেদ, সফিউর রহমান, আবুল বরকত ও আব্দুল জব্বার নামক পাঁচ তরুণ ভাষাপ্রেমী। এঁরা ভাষা-শহিদ।
এই মৃত্যু ও হিংসার রক্ত ভাষা-আন্দোলনকে দেয় গণ-আন্দোলনের জমাট রূপ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন জনপ্রজাতন্ত্রী ‘বাংলাদেশ’-এর আত্মপ্রকাশের মধ্যে এই আন্দোলন সমাপ্ত হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ইউনেসকো (UNESCO) এই ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-এর মর্যাদা দান করলে বঙ্গভাষা এক বিশ্বমাত্রিক মর্যাদায় ভূষিত হয়।