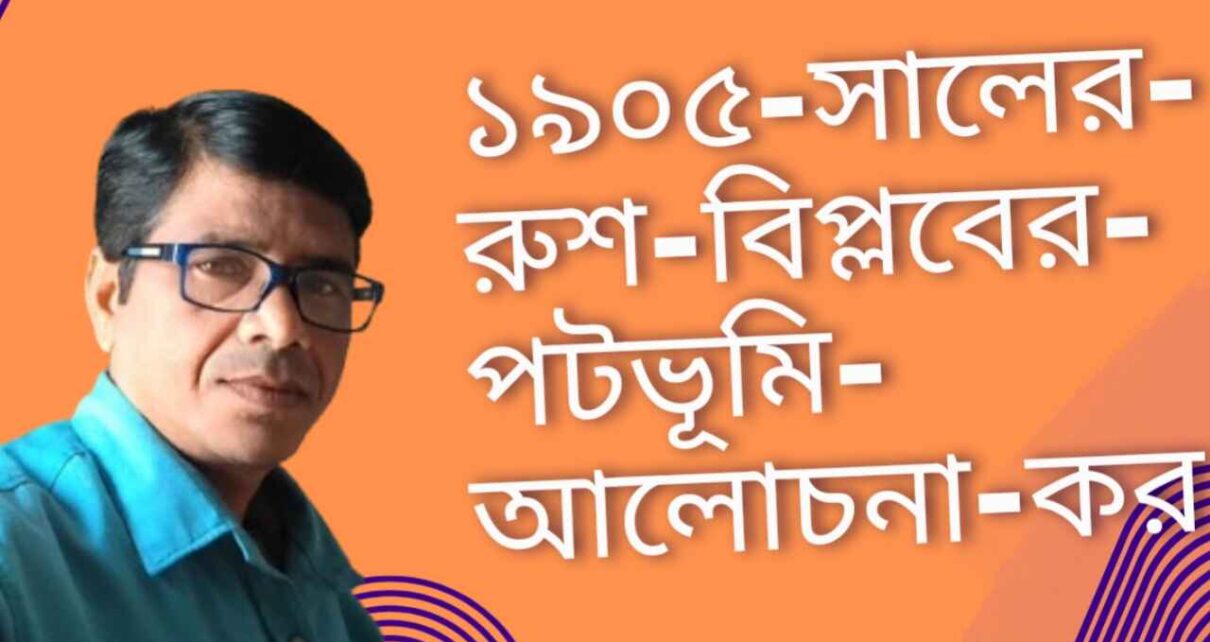১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পটভূমি আলোচনা কর ||
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের কারণ ফলাফল ও গুরুত্ব
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের কারণ ফলাফল ও গুরুত্ব বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব:
১৯০৫ সালের বিপ্লব
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের কারণ :
বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সামন্ততন্ত্রের অন্তরালে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের উদারনৈতিক ভাবধারার সংক্রমণ বাঁচিয়ে রাশিয়া চলছিল। কিন্তু নানা উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া ঝঞ্ঝাক্ষন্ধ হয়ে ওঠে—সংঘটিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব। এই উপাদানগুলিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায়।
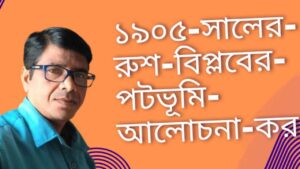
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল:
রাজনৈকি : তিন শতাব্দী ধরে রাশিয়ায় কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। দৈবম্বত্বে বিশ্বাসী জার ছিলেন প্রচলিত রাজনৈতিক ও সমাজব্যবস্থার মধ্যমণি। জারতন্ত্র পরিচালিত হত সৈন্যবাহিনী, স্বৈরশাসন পালিস বাহিনী, ভ,স্বামী অভিজাত শ্রেণী, আমলা ও চার্চের মাধ্যমে। জনপ্রতিনিধিম,লক কোন সংস্থা ছিল না।
গ্রামগুলিতে মীরগুলির কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। এই রকম শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োজন ছিল দক্ষ শাসকের। কিন্তু জার দ্বিতীয় নিকোলাস আদৌ দক্ষ শাসক ছিলেন না। তিনি দেশপ্রেমিক হলেও, দুর্বলচিত্ত এই শাসক রাজত্বের প্রথমদিকে প্রতিক্রিয়াশীল পোবিডোনোস্টেভ ও স্বৈরাচারী প্লেভের প্রভাবাধীন ছিলেন।
রানী আলেকজান্ড্রার বশীভূত হয়ে তিনি বুদ্ধিজীবী-ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকদের সাংবিধানিক সংস্কারের সমস্ত প্রচেষ্টাকে বানচাল করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, নির্বিচার গ্রেপ্তার,
কারাদণ্ড, নির্বাসনদণ্ড এবং বিস্তারিত গ.প্তচর ব্যবস্থার পুনর্গঠন তাঁর শাসনরীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া তিনি জামান, ইহুদী, ফিন, পোল ইত্যাদি অ-রুশ জাতীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে নিম মভাবে রূশীকরণ নীতি অবলম্বন করেন ।
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসন্তোষ :
জারতন্ত্রের এই ঘোর প্রতিক্রিয়াশীলতায় রুশ জনগণের ক্ষোভ পাঞ্জিভত হতে থাকে। ভূমিদাসের মক্তির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ভ,স্বামীরা আশা করেছিল তাদের ত্যাগের বিনিময়ে তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার পাবে। কৃষকরা মীরের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়েছিল।
অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বৈধ স্বীকৃতি না পাওয়ায় ক্ষুধ ছিল। আবার রাশিয়ায় ইউরোপীয় উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার অনঃপ্রবেশ রোধ করা রুশ স্বৈরাচারী শাসকদের শতচেষ্টাতেও সম্ভব হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রশ বদ্ধিজীবীরা গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলন শুর করে।
রুশ শাসকরা দমনমমূলক নীতি অবলম্বন করে। রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ ছিল। এইভাবে নিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার অধিকার না থাকায় বহু গপ্ত রাজনৈতিক সমিতি গড়ে উঠতে থাকে ।
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল:
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে মার্কসিবাদী এই দলটি ‘বলশেভিক (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ও মেনশেভিক (সংখ্যালঘ ) নামে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। বলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবের মাধ্যমে রুশ সমাজের আমলে পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল।
অন্যদিকে নেনশেভিকদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল—প্রথমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তারপর সামাজিক পরিবর্তন সাধন। এছাড়া, আরেকটি উল্লেখযোগ্য দল সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারী দলের কর্মসূচী ছিল— সমস্ত জমিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত করা। কংকদের মধ্যে তারা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিস্তারে মনোযোগী ছিল।
তারা দলের লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে গ্রহণ করে। উদারনৈতিক জমিদার ও বুর্জোয়ারা গঠন করে ‘লিগ অব, এনানসিপেশান’ ( ১৯০৩ খ্রীঃ ) । শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সংস্থাপনই ছিল এর মূল লক্ষ্য। পোল্যান্ড, ইউক্রেন, ল্যাটভিয়া, এস্টোনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সমাজতন্ত্রী দল প্রভাব বিস্তারে সামর্থ হয়।
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের চেষ্টায় প্রকাশিত হয় ‘ইসক্রা’ (ফলিঙ্গ ) নামে পত্রিকা। পত্রিকাটি রুশ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করতে প্রভ‚ত সাহায্য করেছিল । ছাত্র-শিক্ষক-কৃষকদের নানা বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে। এগুলি সমস্তই অবশ্য দমিত হয়ে যায় । এই রাজনৈতিক চেতনার মূলে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ভূমিকাও নগণ্য ছিল না।
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ:
অর্থনৈতিক ঃ
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রাশিয়ায় দ্রুত শিল্পায়ন ঘটলেও তার মলে ছিল বিদেশী মলধনের সাহায্য । ফলে জাতীয় ঋণও বৃদ্ধি পেতে থাকে । হিসেব করে দেখা গেছে ১৮৯৪-১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য ন্ত রুশ সরকারের বিদেশী লগ্নীকারকদের সনদ হিসেবে বার্ষিক দেয় ছিল চল্লিশ কোটি রুবেল । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল চার শ কোটি রবল ।
রাশিয়ার প্রজাশক্তির সিংহভাগ কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরম শোচনীয়। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাসদের মক্তি দিলেও, প্রাক্তন ভূস্বামীদের তুলনায় ‘মীর’গলি কম অত্যাচারী ছিল না । তারা ‘মীর’ ছেড়ে যেতে পারত না বা ইচ্ছামত জমি জায়গা বিক্রি করতে পারত না । শিল্পে-নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা সমভাবেই শোচনীয় ছিল ।
শিল্পবিপ্লবের আদিপর্বে উদ্ভূত সমস্ত কুফল নিয়ে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।’ সে-কারণে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পর্বের বৎসরগুলিতে ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ ও শিল্পে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হতে থাকে ৷ ১৮৯৯ থেকে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ায় শিল্পক্ষেত্রে মন্দা দেখা দেয়। বহ, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা চরম দুর্দশার সম্মখীন হয় ।
এই অর্থনৈতিক মন্দার বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই দূরপ্রাচ্যে রাশিয়া জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যদ্ধের প্রয়োজনে সংরক্ষিত সৈন্য সংগৃহীত হয় গ্রামাঞ্চল থেকে । ফলে কৃষিজ উৎপাদন ব্যহত হয় ও শিল্পে কর্ম সংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায়। রাজনৈতিক দলগলে কৃষক/শ্রমিকদের অসন্তোষকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে ।
সামাজিক : রাশিয়ার সমাজ ছিল দ্বিধাবিভক্ত, একদিকে অভিজাত সম্প্রদায়অন্যদিকে কৃষক/শ্রমিক সম্প্রদায়, যারা ছিল জনসংখ্যার সিংহভাগ। রাজনৈতিক দিক থেকে ভুমিদাস প্রথা উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৃষকদের দঃখদ দশার তান্ত ছিল না। রাশিয়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠেনি তখনও। তাই ম;ষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি ও বিপুল সংখ্যক জনগণের মধ্যে ছিল দস্তর ব্যবধান।
মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের মধ্যে কিছ, সংখ্যক জেম,স্টভোগগুলির মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য দাবি প্রবল হয়ে ওঠে । এরা গণসংযোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয় । এর ফলে আমলাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। রুশ যাজকরা ছিল অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। তারা অর্থ লোল পতা ও পাপাচারের জন্য জনগণের শ্রদ্ধা হারিয়েছিল 1
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ঃ
রুশ-জাপান যুদ্ধে ( ১৯০৪-০৫) রাশিয়ার ধারাবাহিক বিপর্যয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব ত্বরান্বিত করেছিল। যুদ্ধের আরম্ভ থেকেই জনগণ এটিকে রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থবিরোধী হিসেবে গণ্য করেছিল।
জাতীয় অবমাননায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অভ্যুত্থান ঘটায়। নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পথে সাংবিধানিক সংস্কারের দাবি কেবলমাত্র শিক্ষিতজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সাধারণ মানুষও এই দাবিগ লিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে । ‘
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের বিপ্লবের গতি ঃ
রশ শাসনব্যবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সরকারী নির্দেশে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সমস্ত জেম স্টভোর প্রতিনিধিরা সেন্ট পিটার্সবার্গে সমবেত হয় । মতানৈক্য সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ দাবি উত্থাপিত হয়েছিল, যেমন —বিবেক, বাক, মদ্রণ, জনসভা ও সঙ্ঘ স্থাপনের স্বাধীনতা এবং ন্যায়-বিচার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে অধিকতর ক্ষমতা এবং শক্তিশালী পার্লামেন্ট গঠন।
স্বৈরাচারী জার দ্বিতীয় নিকোলাস দাবিগুলিকে উপেক্ষা করলেন । এরপর রুশ-জাপান যদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ে গণবিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করল ।
রক্তমাখা রবিবার: অবশেষে পঞ্জীভূত গণবিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। সেন্ট পিটার্সবার্গের বহু, কলকারখানার শ্রমিকরা ঐ সময় ধর্মঘট করে । ৯ই জানুয়ারী রবিবার গ্রেগরী গ্যাপন নামে জনৈক পাদ্রীর নেতৃত্বে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক তাদের দস্তখৎ সম্বলিত আবেদনপত জারের কাছে পেশ করার জন্য তাঁর শীতকালীন প্রাসাদের অভিমখে শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হয় ।
কেননা এদের অনেকেরই ধারণা ছিল তিনি সহৃদয় হলেও তাদের দূরবস্থার কথা তাঁর অজানা । কিন্তু “জনগণের জনক” জার তাদের দর্শন না দিয়ে সেই প্রাসাদ ত্যাগ করে গেলেন । জারের সৈন্যবাহিনী শোভাযাত্রার পথরোধ করে তার ওপর গলিবর্ষণ করল । এক হাজারেরও অধিক শোভাযাত্রাকারী শ্রমিক নিহত হল, আহত হল আরও অনেক বেশি। ঘটনাটি ইতিহাসে ‘রক্তমাখা রবিবার’ ( Bloody Sunday ) নামে স্বরণীয় হয়ে আছে ।
প্রতিক্রিয়া: ঘটনাটির তাঁর প্রতিক্রিয়া হল । সেন্ট পিটার্সবার্গে সাধারণ ধর্মঘট দেখা দিল এবং তা দ্রুত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। শুরু হল কৃষি হাঙ্গামা। কৃষকরা বহ, অভিজাতদের আবাসস্থলে অগ্নিসংযোগ করে। মে মাসে ইভানোভো-ভজনেসন কস্-এর কাপড়ের কলের ধর্মঘটী শ্রমিকরা একটি সোভিয়েট বা বিশেষ কাউন্সিল নির্বাচিত করে ধর্ম ঘটের নেতৃত্ব দান করে ।
এর সূত্র ধরে রাশিয়ায় বিভিন্ন স্থানে সোভিয়েট গঠিত হতে থাকে পরবর্তীকালে শ্রমিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় এই সোভিয়েটগগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী সংস্থায় পরিণত হয়। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।
জুন মাসে ‘পোটেমকিন’ নামক রণতরীর সৈনিকরা বিদ্রোহ করে। তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈনিকরাও উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের আদেশ সত্ত্বেও গুলিবর্ষণে অসম্মত হয়। বিদ্রোহীদের হাতে জারের প্রতিক্রিয়াশীল খুল্লতাত গ্রান্ড ডিউক সারগাস নিহত হন ।
এই পরিস্থিতিতে ঘোর স্বৈরাচারী জার নরমপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এক ঘোষণাপত্রে তিনি বলেন যে, তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল বা ডুমা আহ্বান করবেন। কিন্তু এটির শুধুমাত্র পরামর্শ দানের ক্ষমতা থাকায় এবং শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখায় এই ঘোষণা জনগণের সন্তোষ বিধান করতে পারে নি।
সুতরাং পর পর সংঘটিত কয়েকটি ধর্ম ঘটে রাশিয়ার জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে অক্টোবর মাসের সাধারণ ধর্মঘট ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য । রেলপথ, বিদ্যুৎ, কলকারখানা, চিকিৎসক ও আইনজীবী এমন কি স্থল ও নৌবাহিনী এই ধর্মঘটের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। এগুলির ওপর শধুমাত্র দমন-উৎপীড়নের নীতির অসারতা জার নিকোলাসও বুঝতে পারলেন ।
সেজন্য ১৭ই অক্টোবর তারিখে এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা সংস্কার ও সাংবিধানিক সরকারের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেন তিনি। কৃষকদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার তীব্রতায় প্রধানমন্ত্রী উইটি শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ভ,স্বামীদের সম্পত্তির অধিকার খর্ব করার চিন্তাও করেন ।
এদিকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ তুঙ্গে ওঠে। মস্কোর শ্রমিকরা বহ, শিল্প কেন্দ্রের ( যেমন রস্টভ-অন-ডন, সরমোভো ) শ্রমিকদের সংগঠিত করে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটায়। জারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটে। বলশেভিক দল বিদ্রোহীদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছিল।
কিন্তু এই বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত অভ্যুত্থানগুলি একটি সংসংহত বিপ্লবের রূপ ধারণ করে নি। স পরিকল্পিত দমননীতির দ্বারা জার সরকার এগুলির কন্ঠরোধ করে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে হিসেব করে দেখা গেছে যে, জার সরকারের এই নৃশংস দমনউৎপীড়নে নিহত হয়েছিল পনের হাজার এবং কারার দ্ধ হয়েছিল সত্তর হাজার ব্যক্তি।
এছাড়াও, অসংখ্য প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ( যেগগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ‘রাশিয়ান পিপলসে লিগ’) পলিস, প্রশাসন এমনকি সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের সাহায্যে ‘প্রোগোম’ সংগঠিত করেছিল অর্থাৎ বিপ্লবীদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশ্য জার ডুমা বা জাতীয় পরিষদ আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।
তাঁর আহত চারটি ডুমার মধ্যে শেষ দুটি ছিল তাঁর একান্ত আজ্ঞাবহ । প্রথম দুটি ( ১৯০৬ ও ১৯০৭ খ্রীঃ) ডুমা বিপ্লবী দলগুলির মতবিরোধের জন্য ভেঙে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এর পরই রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ :
রুশ সরকারের নিষ্ঠুর ও নির্বিচার দমননীতি ও প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা সংগঠিত ‘প্রোগোম’ অভিযানের জন্য ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম
রুশ বিপ্লবের যবনিকাপাত ঘটে। কিন্তু এই বিপর্যয়ের মলে ছিল এই বিপ্লবের অন্তনিহিত দবে’লতা।
প্রথমতঃ বিভিন্ন দলের উদ্দেশ্য কর্মসূচীর বিভিন্নতা
এই বিপ্লবের নেতৃত্বে কোন সংগঠিত দল ছিল না। স্বৈরশাসনের প্রতি সকলেই সমভাবে বিদ্বিষ্ট ছিল, তাই এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনটিকে আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃত গণও আন্দোলন বলে মনে হয়েছিল।
কিন্তু এটি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত ছিল এবং রাজনৈতিক দলগগুলি একযোগে কাজ করলেও তাদের উদ্দেশ্য ও কর্ম পন্থা অনেকক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী ছিল। নারোদনিকিরা সন্ত্রাসবাদী পন্থায় কৃষকদের জন্য জমি ছিনিয়ে নিতে আগ্রহী ছিল। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কৃষকদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিল।
বলশেভিকদের আকাঙ্ক্ষা ছিল গ্রামের মানুষদের সমর্থ ন-লাভ। কিন্তু তাদের সে আশা অপূর্ণ থেকে যায়। তাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মসূচী প্রধানতঃ শিল্প-প্রধান শহরের উগ্রপন্থীদেরই আকৃষ্ট করেছিল। সরকারী শাসনব্যবস্থার বিপর্যয়ের সংযোগে মেনশেভিকরা ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও অন্যান্য অধিকারগুলি দখলের জন্য সচেষ্ট হয় ।
উদারনৈতিকদের সংগঠন ‘লিগ অব এমানসিপেশান’ নতুনভাবে ‘কন্সস্টিটিউশন্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি” ( সংক্ষেপে ‘ক্যাডেট’ ) নামে আত্মপ্রকাশ করে । এর কর্মসূচী হয় সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংবিধান পরিষদ গঠন, সামাজিক সংস্কার ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি।
এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় হিসেবে হিংসাত্মক পদ্ধতির প্রতি তাদের ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। তাই জার কর্তৃক আহত প্রথম ডুমা বা জাতীয় পরিষদে এদের সঙ্গে অক্টোবরিস্টদের মতপার্থক্য চরমে ওঠে। এর পরে দ্বিতীয় ডুমাতেও ক্যাডেট ( এরা ডুমাকে সাংবিধানিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিল) এবং বামপন্থীদের ( এরা বৈপ্লবিক কর্ম সচেীর পক্ষপাতী ছিল ) অনৈক্যের সংযোগে তা প্রধানমন্ত্রী টলিপিন ভেঙে দেন ।
দ্বিতীয়তঃ কৃষক-শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি।
কৃষক-শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাই আন্দোলন স সংহত হতে পারে নি। একথা সত্যি, বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের দেয় ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদান বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল জারকে।
কিন্তু এই আন্দোলনগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। আর জারের মহান, ভবতায় তখনও কৃষকদের আস্থা ছিল । তারা মনে করেছিল জারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে । মোহ তাদের রাজনৈতিক অসচেতনতারই সাক্ষ্য দেয় ।
তৃতীয়তঃ স্থল ও নৌবাহিনী সহযোগী নয়
স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর কিছু কিছ অংশ বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারা বিদ্রোহে অংশ নেয় নি। ভাই জার এদের সাহায্যেই বিপ্লব দমন করেছেন ।
চতুর্থতঃ বৈদেশিক ঋণ,
বিপ্লবের ফলে সন্ত্রস্ত বিদেশী পাঁজিপতিরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ’ অক্ষম রাখতে জারকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ফরাসী ব্যাঙ্কাররা তাঁকে পচাশি লক্ষ ফ্রাঙ্ক ঋণ দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এটি হল মানবেতিহাসে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঋণ। এই ঋণের ফলে জার জনসমর্থ‘নবঞ্চিত হয়েও তাঁর স্বৈরশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন ।
সংগঠিত সংবিধानসত শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা :১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি সঞ্চয়
জার সরকারের দমননীতির কাছে রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব আত্মসমর্পণ করে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের সূচনাতেই এই বিপ্লব স্তিমিত হয়ে আসে। বিপ্লবীদের মধ্যে ভাঙন স্পষ্টতর হতে থাকে, কন্সটিটিউশনাল ডেমোক্রাট বা ক্যাডেটরা পার্লামেন্টকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে চাইল, কিন্তু তাক্টোবরিস্টরা জারের ঘোষণাপত্রে ( অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রীঃ) আস্থাশীল থাকে।
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের শিবিরে অন্তর্দলীয় দ্বন্দ্ব শরে, হয়ে যায়, অন্যদিকে সোশ্যালিস্ট রেভোলিউশনারীরা ষড়যন্ত্র ও হত্যার রাজনীতিতে লিপ্ত থাকে । এ রকম পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।
অভিজাত ভুস্বামী-চার্চ আমলাতন্ত্র-সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি ‘ইউনিয়ন অব দি রাশিয়ান পিপল’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে । এর উদ্দেশ্য ছিল অক্টোবর ঘোষণায় জার-প্রদত্ত উদারনৈতিক শাসনের প্রতিশ্রুতির পরিধি যাতে বিস্তৃত না হয় তার জন্য জারকে সাহায্য করা।
জার কর্তৃক ডুমার ক্ষমতা সকোচনের ব্যবস্থা :
তবু ১৯০৫-এর বিপ্লবী বিস্ফোরণের প্রচ্ছায়ায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁর অক্টোবরের প্রতিশ্রুতি পালনে উদ্যোগী হলেন । অবশ্য প্রথম ভুমা বা জাতীয় সভা আহ্বানের পর্বেই এর ক্ষমতা সঙ্কুচিত করার জন্য দুটি কার্যকর ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করলেন।
একটি ঘোষণা জারি করে প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারী সদস্য-বিশিষ্ট ‘কাউন্সিল অব দি এম্পায়ার নামে জাতীয় সভার ঊর্ধ্ব কক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন আইন ডুমা এবং কাউন্সিলে অননুমোদিত হওয়ার পর জারের অন,মোদনের জন্য তা প্রেরিত হবে। এছাড়া, নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী উইটি ঘোষণা করেন যে, দেশের মৌলিক আইন পরিবর্তনের অধিকার ডুমার থাকবে না।
প্রথম ডুমা ( ১০ই মে থেকে ২২শে জুলাই ১৯০৬ ) :
১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে ডুমার প্রথম অধিবেশন শুরু হল । এতে সব বহৎ দল ছিল ‘কন্সটিটিউশন্যাল ডেমোক্র্যাটরা। সামগ্রিকভাবে ডুমা পশ্চিমী উদারনৈতিক ধাঁচে রাশিয়ার আমলে সংস্কার চেয়েছিল। জারের সম্পর্ণ আজ্ঞাবহ ‘কাউন্সিল অব দি এম্পায়ারের গঠনের পরিবর্তন দাবি করেছিল।
এছাড়া সামরিক আইন উচ্ছেদ ও রাষ্ট্রীয় জমিজমাগলির কৃষকদের দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা দান তাদের অন্যতম দাবি ছিল। সদস্যরা শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলির নির্ভীকভাবে সমালোচনা করেন।
কন্সটিটিউশন্যাল ডেমোক্র্যাটরা জাতীয় সভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা নীতি কার্যকর করার দাবি করলে জার তার প্রবল বিরোধিতা করেন। একটি সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দেয় ৷ জার “জনগণের প্রতিনিধিরা নিজ অধিকার বহির্ভূত বিষয়ে বিপথগামী” হওয়ার অজুহাতে প্রথম ডুমা ভেঙে দিলেন ( ২২শে জুলাই, ১৯০৬ খ্রীঃ ) ।
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন আরম্ভ হবে ঘোষিত হয়। স্টলিপিন প্রধানমন্ত্রী নিক্ত হন। প্রথম ডুমার বহ, সদস্য ফিনল্যান্ডে আশ্রয় নেয় । তারা ভাইবর্গ’ থেকে ২৩০ জন সদস্য-স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র জারি করে।
এতে প্রথম ডুমা ভেঙে দেওয়ার বিরদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। করদান বা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান না করতে জনগণকে আহ্বান জানান হয়। কিন্তু এই ‘ভাইবর্গ’, ঘোষণাপত্র’ জনগণের মধ্যে আশানরূপ সাড়া জাগাল না। রুশ সরকার ততদিনে বিপ্লবের ধাক্কা সরকার নির্বাচনে কারচুপি করায় ‘কন্সটিটিউশন্যাল ডেমোক্র্যাটদের’ সামলে উঠেছে। নির্বাচিত প্রতিনিষিদের সংখ্যা অভাবনীয়ভাবে হ্রাস পেল ।
দ্বিতীয় ভুমা: নির্ধারিত দিনে দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন শুরু হল । প্রথম থেকেই মন্ত্রিসভার সঙ্গে ডুমার বিরোধ শব্দ হয়। অবশেষে রুশ সরকার বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য ষোলজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। সাংবিধানিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে তুমা উত্তাল হয়ে ওঠে। জার দ্বিতীয় তুমা ভেঙে দিলেন ( ১৬ই জুন, ১৯০৭ খ্রীঃ)।
এর পর প্রধানমন্ত্রী স্টীলপিন নির্বাচন আইন এমন ভাবে পরিবর্তিত করে দেন যে, কৃষক-শ্রমিকদের ভোটাধিকার সঙ্কুচিত হয়ে যায়, ডুমা পরিণত হয় উচ্চশ্রেণীর এক নির্বাচিত সংসদে ।
তৃতীয় ডুমা (১৯০৭ ১৯১২): নব-নির্বাচিত তৃতীয় ডুমার অধিবেশন শুরু হল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে। জারের আজ্ঞাবহ প্রধানতঃ ভূস্বামীদের এই পরিষদ পাঁচ বৎসর স্থায়ী হয়েছিল । এর একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ‘মীরে’র কর্তৃত্বের অবসান (স্টলিপিন প্রতিক্রিয়া দ্রষ্টব্য)। ঘটিয়ে কৃষকদের জমির স্বত্ত্ব-স্বামিত্ব দান
চতুর্থ ডুমার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল প্রতিক্রিয়াশীলরাই। অবশ্য ‘অক্টোবরের ঘোষণা’ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচিত হয় নি–এই অজ হাতে অক্টোবরিস্টরা জার সরকারের বিরোধিতা শরু করে । ক্রমে সংস্কার আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে । ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘প্রোগ্রেসিভ ব্লক’ নামে এক সংস্কারবাদী দল গড়ে ওঠে।
জারের স্বৈরশাসন-বিরোধী মনোবৃত্তি সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে সংক্রামিত হয় । এর অনিবার্ষ পরিণতি হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লবে । এর ফলে জারতন্ত্রের চিরতরে বিলুপ্তি ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রথম সাম্যবাদী সরকার ।
স্টীলপিন প্রতিক্রিয়া:
দ্বিতীয় নিকোলাসের মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্টীলপিন ১৯০৬ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত ছিলেন । অন্তরে রক্ষণশীল হলেও প্রয়োজনবোধে উদার নীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের পরই তিনি নির্বিচার দমননীতির সাহায্যে সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লববাদীদের স্তব্ধ করে দেন ।
১৯০৫ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শস্যহানি, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থানে স্যানে দদূর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব কৃষকদের বৈপ্লবিক মনোভাবকে বর্ধিত করেছিল। ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য ন্ত বহ, কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল — সারা দেশে অগ্নিকাণ্ড, লঠতরাজ ইত্যাদির তাণ্ডব চলেছিল। অগণিত কৃষক ও বিপ্লবীদের রক্তস্নানে সরকার বিপ্লব দমন করে ৷
অন্ততঃ কিছু সংখ্যক কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল — ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়েছিল ‘কৃষক ইউনিয়ন’ নামে একটি দল। প্রথম ডুমাতেই এক কৃষক প্রতিনিধি ভূস্বামীদের উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে বলেছিল যে, তারা তাদের জমি চুরি করেছে। সতরাং তারা জমি ক্রয় করে নয়, ছিনিয়ে নেবে । প্রবল ভূমিক্ষধা নয়, তাদের সচেতনতারও সাক্ষ্য বহন করে । উক্তিটি শখে, কৃষকদের
মীরের নিয়ন্ত্রণ লোপ: স্টলিপিন তাই বুঝেছিলেন ভূমি সমস্যার সমাধান কত জরুরী। তাঁর দৃষ্টিতে কৃষকদের অসন্তোষের মেেল হল মরি বা গ্রাম্যসমিতিগলির কৃষক ও কৃষি উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ । সুতরাং স্টীলপিনের আইন সংস্কারের প্রথম উদ্দেশ্য হল এই নিয়ন্ত্রণ বিলপ্ত করা।
সমষ্টিগতভাবে কৃষকদের জমি ভোগদখলের পরিবর্তে কৃষকদের জমির ব্যক্তিগত মালিকানাত্ব দান । এ ব্যাপারে কৃষকদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জমির মালিকানা না দিয়ে জমির চকবদ কিরণ এবং তা বংশান ক্রমিক করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।
কৃষকদের ভূ-সম্পত্তিবৃদ্ধির সুযোগ: স্টলিপিন সংস্কারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল কৃষকরা যাতে সহজে ভ,স্বামীর বা সরকারী জমি ক্রয় বা খাজনার পরিবর্তে ভোগদখলের অধিকার পায় তার ব্যবস্থা করা। এই অননুসারে কৃষকদের জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাঙ্কগগুলির কর্ম’ পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা হল যাতে তারা সহজে ঋণ পায়। গ্রাম্য ঋণদানকারী সমিতিও গড়ে তোলা হয় ৷
অনাবাদী অঞ্চলে কৃষকদের বসতিস্থাপন:
স্টীলপিন সংস্কারের তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের ভূমিক্ষধা নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত ভ,মিষ,ক্ত অনাবাদী অঞ্চলে ( যেমন সাইবেরিয়া) কৃষকদের বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করা। কৃষকদের গমনাগমনের ওপর মীরগগুলির পরোন নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হয় । করধার্য ও কর সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে মীরগগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
গুরুত্ব: স্টলিপিন সংস্কারের ফলে মধ্যগীয় কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে । কৃষিযন্ত্র ও কৃত্রিম সার প্রয়োগ করা হতে থাকে । কিন্তু কৃষির এই উন্নতি কয়েকটি স্থানে এবং বড় বড় জোতদারের খামারে সীমাবদ্ধ ছিল । আর ‘কুলাক’ যা বড় বড় জোতদারের কাজেই ভুসম্পত্তি বৃদ্ধির সংযোগ সম্প্রসারিত হয়েছিল।
সাধারণ কৃষকদের সিংহভাগেরই জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে নি। তব, ঐতিহাসিক ক্রেগের মতের প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে, ভ,মিদাসদের মুক্তির ঘোষণার পর স্টীলপিনের সংস্কার একটি গরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।
সংস্কারের ত্রুটি: স্টলিপিনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, তাঁর প্রবর্তিতে সংস্কারের যুক্তিসঙ্গত সীমানায় পৌঁছতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল। কেননা অন্তরে তিনি উদারনৈতিক ছিলেন না। অথচ প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁকে উদারপন্থী বলে নিন্দা করেছে । অবশেষে এক আততায়ীর হাতে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায় ( ১৯১১ খ্রীঃ)।
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের ফলাফল ও গরুত্ব:
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ফলাফল ও গরুত্ব
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব রাশিয়ার ইতিহাসে একটি গরুত্বপূর্ণ দিক-চিহ্ন। এই বিপ্লব ব্যথ’ হলেও একেবারে নিষ্ফল হয় নি । জারতন্ত্র রক্ষা বিপ্লবের শিক্ষা পেয়েছিল বটে কিন্তু এর ভিত্তিমূল কেপে উঠেছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর জুমা দূর্বল ও রক্ষণশীল হয়ে পড়লেও এর মধ্য
অর্ধ’-সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।
প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাগগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠলেও এই শাসনব্যবস্থাকে সমূলে বিনাশ করতে পারে নি। বিপ্লব জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার উদ্দীপকের কাজ করেছিল । জনগণ যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করেছিল তা তাদের ভবিষ্যৎ মক্তি-আন্দোলনে প্রভূত সাহায্য করেছিল। বিপ্লব চলাকালে সৈনিকরা ছোট ছোট ‘বিপ্লবী কাউন্সিল’ ও শ্রমিকরা বিভিন্ন অঞ্চলে ‘সোভিয়েট’ নামে বহু সংগঠন গড়ে তুলেছিল।
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সফল অক্টোবর বিপ্লবের সময় এই ধরনের সংগঠনগালি কার্যকর ভ‚মিকা নিয়েছিল। লেনিন যথার্থই বলেছেন, “১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সাল ব্যতীত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য সম্ভব ছিল না।”
কৃষকশ্রেণীর ওপর প্রতিক্রিয়া: শহরের শ্রমিকশ্রেণী অবশ্য বিপ্লব থেকে প্রত্যক্ষ সফল লাভ করে নি। জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটে নি। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার স্বীকৃত হলেও বিপ্লব চলাকালে সংগঠিত শ্রমিক সংগঠনগগুলি রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ হয়। রাশিয়ায় পশ্চিমী ধাঁচের শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। নির্বিচার দমননীতিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল, কিন্তু বিপ্লবী চেতনার প্রবাহ শঙ্ক হয়ে যায় নি ৷
শ্রমিকশ্রেণীর ওপর প্রতিক্রিয়া: – কিন্তু কৃষকরা – বিশেষতঃ তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক — বিপ্লবের দ্বারা নিজেদের পরষ্কৃত করতে পেরেছিল। ১৯১৭-পূর্বে দশ বৎসরে কৃষি ও কৃষকদের সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয় । মীরের অধীনে কৃষকদের সমষ্টিগত ভ-সম্পত্তির মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয়েছিল।
কৃষকদের ওপর মীরের নিয়ন্ত্রণ উচ্ছেদ করা হয় । কৃষকরা জমির চকবন্দীকরণের সংযোগ পেয়েছিল, এমন কি এগুলির ওপর বংশান ক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে । যাতে তারা জার বা জমিদারের কাছ থেকে জমি কিনতে বা ইজারা নিতে পারে তার জন্য কৃষক ভূমি ব্যাঙ্কগালির কর্ম পদ্ধতি সংস্কার করা হয় । তাদের ভ‚মিক্ষ,ধা নিবারণের জন্য সাইবেরিয়া বা অন্যত্র বসতি স্থাপনের সংযোগ দেওয়া হয় ।
উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃত্রিম সারের ব্যবহার, কোন কোন অঞ্চলে বহু, অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য জমিতে পরিণত করা ইত্যাদির ফলে উৎপাদনবদ্ধি ঘটে । কিন্তু স,ফল ভোগ করেছিল মুষ্টিমেয়রাই, কৃষকদের অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান খুব নীচে ছিল। তব, স্টলিপিনের সংস্কারের ফলে কৃষকদের দীর্ঘ—-সঞ্চিত অভিযোগগগুলি কিছ, পরিমাণে দূর হয়েছিল ।
রুশীকরণের তীব্রতা বৃদ্ধি : সংখ্যালঘু, জাতিগলির পক্ষে এই বিপ্লবের ফলাফল আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। তাদের অভিযোগগগুলি দূর করার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ফিনল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া হয়, সেখানে রশীকরণ নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।
কুখ্যাত ‘ব্ল্যাক হানড্রেডস’ নামে এক উগ্র রশ জাতীয়তাবাদী দল ইহুদীদের ওপরে অকথ্য নির্যাতন চালায় । পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্টোনিয়া, ইত্যাদি স্থানে রূশীকরণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ৷
নিরক্ষরতা দূরীকরণ : ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দলটি আনষঙ্গিক ফল উল্লেখযোগ্য। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য চার্চ-বিদ্যালয়ের প্রবল বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হয় । শিক্ষাখাতে এই প্রথম রংশ সরকার বঙ্গ অর্থ— মঞ্জুর করেছিল । অবশ্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পর্বে রাশিয়ায় নিরক্ষরদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি ছিল।
দ্বিতীয়তঃ, এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার জানলাতন্ত্র মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। বিপ্লব চলাকালের মর্যাদানাশের প্রলম্বিত ছায়া এর ওপর পড়েছিল । এছাড়া, পুনরায় বৈপ্লবিক অভ্যূত্থানের আশঙ্কায় আমলারা স্বেচ্ছাচারী হতে পারতো না ।
অবশ্য জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সীমা আমলাদের খেয়ালখুসীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। সতরাং এই বিপ্লবের ফলে বিপ্লবীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ,তি´ ঘটে নি। সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থকতার জন্য রাশিয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক বৃহত্তর বিপ্লবের পথে এগিয়ে যায় । আমলাতন্ত্রের ওপর প্রতিক্রিয়া
রুশ পররাষ্ট্র নীতি (১৮৮১-১৯১৭ খ্রীঃ ) : ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের
তৃতীয় আলেক- জান্ডারের রাজত্বকাল: জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালের পররাষ্ট্রক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল রশ-ফরাসী মৈত্রী । ১৮৯৩ খ্রীঃ)। ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গঠিত হওয়ার পর বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সকে ইউরোপে নির্বান্ধব রাখা।
বিসমার্ক” যতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন তাঁর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। তাঁর কটেনৈতিক মোহজালে আবদ্ধ রাষ্ট্রগলি ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলতে পারে নি বা চায়নি। অবশ্য নিকট-প্রাচ্যে রুশ-অস্ট্রিয়া দ্বন্দ্বে তিনি অস্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করেন ৷ ফলে রাশিয়া জার্মানীর ওপর অসন্তুষ্ট হয় । কুটকৌশলী বিসমার্ক’ রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী অক্ষর রাখেন ।
কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়নের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং অস্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্ব রাশিয়াকে শঙ্কিত করে তোলে । এছাড়া, রশ মৈত্রীর ওপর তিনি গরুত্ব আরোপ করেন নি। তাই তিনি রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ গঠনমূলক কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ হিসেবে দিতে অস্বীকৃত হন। রাশিয়া তখন ক্রাশঃ ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকতে থাকে ।
এর ফলে রাশিয়া তার স্থলবাহিনী, নৌবহর ও রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর ফরাসী ঋণ লাভ করে । সে-কারণে জার তৃতীয় আলেকজান্ডার ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের বিরোধী হলেও ফ্রান্সের সঙ্গে নৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ এর ফলে ফ্রান্স তাঁর নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে ওঠে, আর জানানীঅস্ট্রিয়া চক্রান্তে রাশিয়া কোণঠাসা অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে ।
দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকাল: পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে জার দ্বিতীয় নিকোলাস শান্তিবাদী ছিলেন। জার্মান রাজপরিবারে তিনি বিয়ে করেছিলেন, জার্মানীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল। তব, ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী তিনি অক্ষম রাখেন। তিনি ও জারিনা প্যারিস সফরে গেলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। তিনি বলেছিলেন যে, র,শ-সাম্রাজ্য ও ফরাসী তৃতীয় প্রজাতন্ত্র এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ । চীনে মাও,রিয়ার ওপর রাশিয়ার লব দৃষ্টি পড়েছিল।
কিন্তু ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করে মারিয়া অধিকার করে। চীনের ওপর জাপানের এই প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় সেখানে রুশ-স্বার্থ— বিঘ্নিত হয় । অবশেষে রাশিয়ার উদ্যোগে সিমনোশেকির সন্ধিতে প্রাপ্ত পোর্ট আর্থার ও লিয়াওটাং জাপান ক্ষতিপরণের বিনিময়ে চীনকে প্রত্যর্পণ করে ৷
মাঞ্জুরিয়ায় রুশ আধিপত্য বিস্তারের উদ্যোগ: মাঞ্জুরিয়ায় প্রত্যাশিত রশ আধিপত্য বিস্তারের সংযোগ এনেছিল বক্সার বিদ্রোহ ( ১৯০০ খ্রীঃ)। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিবর্গের বিরোধিতা ও ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর ( ১৯০২ খ্রীঃ) ফলে রাশিয়া ধাপে ধাপে মারিয়া থেকে সৈন্য অপসারণের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় ৷
প্রথম কিস্তি সৈন্য অপসারণের পর রাশিয়া পুনরায় মাঞ্জুরিয়ায় নিজ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয় ৷ এতে নিজ স্বার্থ বিপন্ন হওয়ায় জাপান রাশিয়াকে চরমপত্র প্রেরণ করে। রাশিয়া চরমপত্র গ্রহণে অস্বীকার করলে রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫) শর, হয় ।
এই যুদ্ধে ‘বামন’ জাপান রুশ দৈত্যকে উভয়ের মধ্যে পোর্টসমাউথের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে সুদূর-প্রাচ্যে রশ অগ্রগতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয় । যুদ্ধের বিপর্যয়ের ফলে জারতন্ত্রের প্রতি জনরোষ বৃদ্ধি পায়।
ইঙ্গ-বুশ করভেনশন (১৯০৭ ): পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে র,শ-ফরাসী মৈত্রীর পর রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ইঙ্গ-রশ কনভেনশন (১৯০৭ খ্রীঃ)। পারস্য, আফগানিস্থান ও দূরপ্রাচ্যে ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে স্বার্থ—-সংঘাত বাঁধে । অভিন্ন শত্রু, জার্মানীর বিরোধিতার জন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা কমতে থাকে।
অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে ইঙ্গ-রশ কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় । এর দ্বারা পারস্যকে রুশ ও বৃটিশ দুটি প্রভাব বলয়ে বিভক্ত করা হয় ; রাশিয়া আফগানিহান ও তিব্বতে হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয় ৷ ফলে ইংরেজদের ভারতবর্ষে রুশ অগ্রগতির ভীতি বিদারিত হয়।
এইভাবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া সম্মিলিত হয়ে একটি কটনৈতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলে। এটি ত্রিপল আঁতাত নামে অভিহিত। ত্রিপল অ্যালায়েন্সের প্রত্যন্তর হিসেবে এটি গড়ে উঠেছিল। অবশেষে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়া:
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে রাশিয়ার একটি ভূমিকা ছিল। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার কাছে চরমপত্র প্রেরণ করলে রাশিয়া সার্বিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করে। ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করে । কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের ( ১৯১৭ ) জন্য রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে বেস্টলি টোভস্ক-এর সন্ধি স্বাক্ষর করে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে